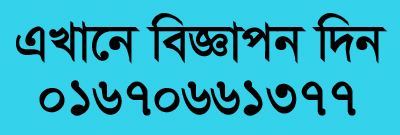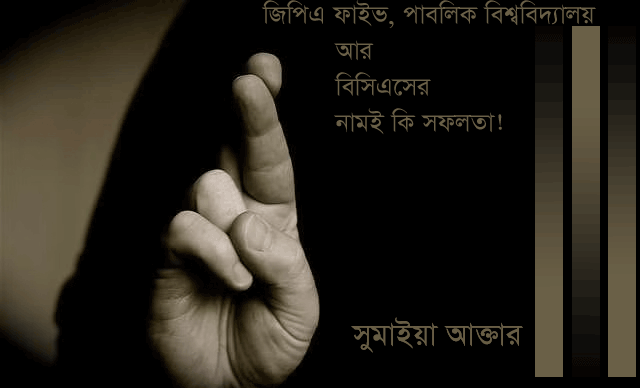শৃঙ্খলার নিগূঢ় থেকে মুক্তিই প্রত্যাশা
“আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব”
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানটিতে রূপের থেকে ভালোবাসাকেই বড় করে দেখেছেন। সেই সাথে দৈহিক শক্তির থেকে গুণ টিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কবি প্রাধান্য দিয়ে থাকলেও একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে কি আমরা সত্যি রূপকে পিছনে ফেলে গুণের দাঁড় বেয়ে জীবন নৌকাতে কি এগিয়ে যেতে পারছি নারীরা! পারছি কি আমাদের মেধাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে। আমাদের সুস্থ সুন্দর মানসিকতা এবং সৃজনশীল চিন্তা ভাবনা কি মিলিয়ে দিয়েছে নারীর মুক্তি! আমরা নারীরা আমাদের মেধা শক্তি, পরিশীলিত মন এবং সৃজনশীল চিন্তা ভাবনা দিয়ে পারছি জায়গা করে নিতে! না কি এখনও আমরা আটকে আছি “মেয়েটা ভালো কিন্তু গায়ের রং বেশ চাপা, একটু মোটা আর খাটো”-এই বাক্যের মধ্যেই।
গোটা বিশ্ব এগিয়ে গেছে, আর্টিফিসিয়াল ইন্ট্যালিজেন্স এর যুগে প্রবেশ করে আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেও নারীকে কখনোই তার মেধা, পরিশ্রম, সৃজনশীলতা দিয়ে বিচার করতে পারি না। নারীর কথা আসলেই একটা বিষয় মাথায় চলে আসে তা হলো তার রূপ। নারীর রূপটাকে আমরা এমনভাবে কদর করি যেন রূপ ছাড়া নারী কপর্দকশূন্য।
চাকরির বাজার থেকে শুরু করে বিয়ের বাজার সর্বত্রই নারীর রূপ যেন নারীকে বিচারের মানদণ্ড। যে নারীর রূপ নেই, তার সকল গুনাবলি মেধা সবকিছুই আমাদের কাছে নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা মস্তিষ্কহীন রূপবতীকে মাথায় তুলতে পারলেও যোগ্যতাসম্পন্ন তুলনামূলক কম রূপসী নারীকে মূল্যহীনই মনে করি। প্রকৃতপক্ষে যদি আমরা নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেই থাকি তবে কি আমাদের উচিত তার রূপের উপর নির্ভর করে তার মূল্য যাচাই করা! এক্ষেত্রে কি আমরা নারীকে সামগ্রী হিসেবে মিলিয়ে ফেলছি না! একজন মানুষ গণ্য হবে তার মানবতা, মানসিকতা, মেধা, সৃজনশীলতা দিয়ে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের ক্ষেত্রে মেধা-মননের স্বার্থকতা থাকলেও নারীর সেই দাম পেতে হলে চড়া মূল্য দিতে হয়। কারণ আমরা নারীদের বিবেচনাই করি কিছু বিশেষণে। আমাদের কল্পনার জগতের রমণীরা সবসময়ই হয় লম্বা-ছিপছিপে, লাউয়ের ডগার মতো দেহ, দুধে আলতা গায়ের রং নিয়ে খিলখিল করে বাঁকা চোখে তাকিয়ে থাকা চঞ্চলা। আমাদের চিন্তা ভাবনাতেই সৌন্দর্যের জয়জয়কার। কিন্তু যখন একজন স্থুলকায় বিশেষ বিশেষণ ব্যবহার করার মতো যার সেরকম রূপ নেই সেই নারীকে আমরা কখনো তার প্রাপ্য সম্মানটুকুম এবং তাঁর মেধার-মননের প্রেমেও মুগ্ধ হতে পারি না।
আর কতদিন! আর কত! আমরা নারীকে কবে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে মূল্য দিতে শিখবো। কবে নারীকে তার কর্মে, মেধায় বিচার করতে পারব। সেদিন নারীর শারীরিক সৌন্দর্য হবে গৌণ, তার মেধা, মানসিকতা সর্বোপরি মানুষ হিসেবে নারী কেমন সেটাই হয়ে উঠবে মুখ্য। আমরা মানুষ হিসেবে বিচার করব তাদের। নারীর সম্মান দিব তার মানসিকতা, পরিশীলিত মন ও মেধা দিয়ে সেদিনই তো সমাজে রূপের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তি ঘটবে নারীর।
লেখক: রায়হাতুল জান্নাত প্রত্যাশা
লোক প্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সহকারী শিক্ষক
উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
|

“আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব”
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানটিতে রূপের থেকে ভালোবাসাকেই বড় করে দেখেছেন। সেই সাথে দৈহিক শক্তির থেকে গুণ টিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কবি প্রাধান্য দিয়ে থাকলেও একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে কি আমরা সত্যি রূপকে পিছনে ফেলে গুণের দাঁড় বেয়ে জীবন নৌকাতে কি এগিয়ে যেতে পারছি নারীরা! পারছি কি আমাদের মেধাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে। আমাদের সুস্থ সুন্দর মানসিকতা এবং সৃজনশীল চিন্তা ভাবনা কি মিলিয়ে দিয়েছে নারীর মুক্তি! আমরা নারীরা আমাদের মেধা শক্তি, পরিশীলিত মন এবং সৃজনশীল চিন্তা ভাবনা দিয়ে পারছি জায়গা করে নিতে! না কি এখনও আমরা আটকে আছি “মেয়েটা ভালো কিন্তু গায়ের রং বেশ চাপা, একটু মোটা আর খাটো”-এই বাক্যের মধ্যেই।
গোটা বিশ্ব এগিয়ে গেছে, আর্টিফিসিয়াল ইন্ট্যালিজেন্স এর যুগে প্রবেশ করে আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেও নারীকে কখনোই তার মেধা, পরিশ্রম, সৃজনশীলতা দিয়ে বিচার করতে পারি না। নারীর কথা আসলেই একটা বিষয় মাথায় চলে আসে তা হলো তার রূপ। নারীর রূপটাকে আমরা এমনভাবে কদর করি যেন রূপ ছাড়া নারী কপর্দকশূন্য।
চাকরির বাজার থেকে শুরু করে বিয়ের বাজার সর্বত্রই নারীর রূপ যেন নারীকে বিচারের মানদণ্ড। যে নারীর রূপ নেই, তার সকল গুনাবলি মেধা সবকিছুই আমাদের কাছে নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা মস্তিষ্কহীন রূপবতীকে মাথায় তুলতে পারলেও যোগ্যতাসম্পন্ন তুলনামূলক কম রূপসী নারীকে মূল্যহীনই মনে করি। প্রকৃতপক্ষে যদি আমরা নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেই থাকি তবে কি আমাদের উচিত তার রূপের উপর নির্ভর করে তার মূল্য যাচাই করা! এক্ষেত্রে কি আমরা নারীকে সামগ্রী হিসেবে মিলিয়ে ফেলছি না! একজন মানুষ গণ্য হবে তার মানবতা, মানসিকতা, মেধা, সৃজনশীলতা দিয়ে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের ক্ষেত্রে মেধা-মননের স্বার্থকতা থাকলেও নারীর সেই দাম পেতে হলে চড়া মূল্য দিতে হয়। কারণ আমরা নারীদের বিবেচনাই করি কিছু বিশেষণে। আমাদের কল্পনার জগতের রমণীরা সবসময়ই হয় লম্বা-ছিপছিপে, লাউয়ের ডগার মতো দেহ, দুধে আলতা গায়ের রং নিয়ে খিলখিল করে বাঁকা চোখে তাকিয়ে থাকা চঞ্চলা। আমাদের চিন্তা ভাবনাতেই সৌন্দর্যের জয়জয়কার। কিন্তু যখন একজন স্থুলকায় বিশেষ বিশেষণ ব্যবহার করার মতো যার সেরকম রূপ নেই সেই নারীকে আমরা কখনো তার প্রাপ্য সম্মানটুকুম এবং তাঁর মেধার-মননের প্রেমেও মুগ্ধ হতে পারি না।
আর কতদিন! আর কত! আমরা নারীকে কবে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে মূল্য দিতে শিখবো। কবে নারীকে তার কর্মে, মেধায় বিচার করতে পারব। সেদিন নারীর শারীরিক সৌন্দর্য হবে গৌণ, তার মেধা, মানসিকতা সর্বোপরি মানুষ হিসেবে নারী কেমন সেটাই হয়ে উঠবে মুখ্য। আমরা মানুষ হিসেবে বিচার করব তাদের। নারীর সম্মান দিব তার মানসিকতা, পরিশীলিত মন ও মেধা দিয়ে সেদিনই তো সমাজে রূপের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তি ঘটবে নারীর।
লেখক: রায়হাতুল জান্নাত প্রত্যাশা
লোক প্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সহকারী শিক্ষক
উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
|
|
|
|

কলমে : শিপারা শিপা
ডিজিটাল বাংলাদেশ, বর্তমানে সবদিক দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার হারও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে অবশ্যই এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আজকাল পত্রিকার পাতায়ও বিভিন্ন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, যেমন ড্রাইভার নিয়োগ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদিতে আয়া, বয়, নাইট গার্ড নিয়োগ, ইত্যাদির ব্যাপারে শিক্ষাগত যোগ্যতা যেমন, এসএসসি, অষ্টম শ্রেণী কিংবা পঞ্চম শ্রেণী পাশ প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। আমিও মনে করি দেশ কিংবা সমাজের উন্নয়নে অবশ্যই সর্ব ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজন। তাছাড়া প্রতি বছর সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রচুর বরাদ্দ দিয়ে থাকেন। মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ, বৃত্তি উপবৃত্তিরও সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তবে কেন শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে।
দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের দেশের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার কি কোন প্রয়োজন নেই?
আমাদের দেশের কিছু জনপ্রতিনিধিদের আচার আচরণ, কাজকর্ম দেখে মাঝে মাঝে অবাক হতে হয়, আর ভাবতে থাকি হয়তো তাদের মাঝে শিক্ষার অভাব, তাইতো সমাজের উন্নয়ন না করে নিজ সংসারের উন্নয়নে ব্যস্ত থাকেন তারা। তাই আমি মনে করি জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে যোগ্যতা ও নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম থাকা জরুরি, যা দেশের স্বার্থে।
একজন জনপ্রতিনিধি উচ্চ শিক্ষিত না হলেও মোটামুটি শিক্ষিত হওয়া দরকার। তবে মেয়র পদে কমপক্ষে স্নাতক বা এইচএসসি, কাউন্সিলর পদে এইচএসসি বা এসএসসি এই রকম নিয়ম করলে যোগ্য ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের কাজে নিয়োজিত হয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।
স্বশিক্ষিত বলতে বুঝা যায়, নিজে নিজে যতটুকু সম্ভব ততটাই পড়েছেন বা হতে পারে পঞ্চম, অষ্টম বা শুধুমাত্র নাম দস্তখত অথবা টিপসই জানা লোক। মনে প্রশ্ন জাগে এতো কম শিক্ষিতজনেরা কিভাবে জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করবেন, কিভাবে নগর উন্নয়ন করবেন যেহেতু এসব কাজে অবশ্যই জ্ঞানের দরকার, আর জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার দরকার। সমাজের উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা কিভাবে এদের মূল্যায়ন করবেন?
একজন গ্রাজুয়েট, মাস্টার্স কিংবা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষা অফিসার সহ সমাজের অন্যান্য উচ্চপদস্থ লোকেরা তাদের মহামূল্যবান ভোট স্বশিক্ষিত, পঞ্চম বা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করা প্রার্থীকে দিয়ে জয়যুক্ত করবেন এটি অত্যন্ত বেমানান।
এসব ব্যাপারে ভাবা দরকার কেননা দেশে শিক্ষিত লোকের অভাব নেই। জনপ্রতিনিধি করতে হলে তার নৈতিক চরিত্র, অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে যাচাই বাছাই করা অবশ্যই দরকার।
এসবের পরিবর্তন হওয়া জরুরি, একজন জনপ্রতিনিধি প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।
|
|
|
|

সুধীর বরণ মাঝি
শিক্ষক
হাইমচর সরকারি মহাবিদ্যালয়
হাইমচর, চাঁদপুর।
পৃথিবীর সকল সভ্যতা, ইতিহাস, উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূলে রয়েছে নদী। নদী সভ্যতাকে আধুনিক করেছে। মানুষ অপার সম্ভাবনা নিয়ে বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলেছে। আজকের আধুনিক সভ্যতায় নদীর ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের ইতিহাস সভ্যতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে। নদী আমাদের বিশাল গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। এর অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর দেশ রেখে যেতে পারি।বাংলাদেশে নদীমাতৃক দেশ। নদীমাতৃক বাংলাদেশ উপাধি যেন আজ প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে! নদীগুলো অধিকংশই ‘ কঙ্কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষ নিজেদের সামান্য স্বার্থে অসেচেতন ভাবে সুদূও প্রসারী ক্ষতির চিন্তা না করে নদী খালগুলো ভরাট করে ফেলছি, দখলে নিয়ে নিচ্ছি। আমাদের হীন স্বার্থের মানসিকতার ভয়াবহ পরিণতি রেখে যাচ্ছি আমাদের আদরের আগামী প্রজন্মের জন্য। এদেশের আনাছে-কানাছে ছিল হাজারো নদী। একসময় এদেশে প্রায় ১২শ নদী ছিল। এখনা যা ২৩০ এ দাঁড়িয়েছে। যে নদীগুলোর জীবন প্রদীপ এখনো টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে, সেগুলো থেকে এখনো মানুষ পাচ্ছে কাঙ্কিত সুফল।
নদী আমাদের জাতীয় সম্পদ। একে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার, আপনার, সরকার-রাষ্ট্র এবং সবার। প্রাচীন কাল থেকেই এদেশের মানুষের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম নৌপথ। যাতায়ত এবং পণ্য পরিবহনে নিরাপদ, সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী হওয়ায় মানুষ এই খাতকে বেছে নেয়। আমাদের নৌ পরিবহন খাত এক অমিত সম্ভাবনাময় খাত। সময়ের চাহিদা বিবেচনায় রেখে একে ঢেলে সাজানোর এখনিই উপযুক্ত সময়।
নৌপরিবহনকে সহজলভ্য, আরামাদায়ক, আধুনিকায়ন করতে এ খাতের ঝঞ্জাট দূর করা করা প্রয়োজন। স্বাভাবিক ভাবেই সড়ক পরিবহন থেকে নৌপরিবহন অনেক স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ, সাশ্রয়ী, আরামদায়ক এবং আনন্দদায়কও বটে। কোন এক দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) ড্রেজিং প্রকল্পে নীরব বিপ্লব ঘটাতে চলছে। ১৫টি নৌরুটে ৩১টি ড্রেজার খনন কাজে নিয়োজিত আছে। খননে ইতোমধ্যে মৃত নদীর নাব্য ফিরেয়ে আনা হয়েছে ১হাজার ৮০০কিলোমিটার নৌপথ। পাশপাশি নদীর খননে উত্তোলনকৃত মাটি দিয়ে ৫হাজার একর অকৃষি জমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) ড্রেজিং প্রকল্পের পরিসর বৃদ্ধি করে খনন প্রক্রিয়া চলমান রাখতে পারলে একদিকে যেমন নদীর নাব্যতা সংকট দূর হবে তেমনি অন্যদিকে বৃদ্ধি পাবে আমাদের কৃষি জমির পরিমাণ, কৃষি উৎপাদন এবং নতুন নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবে।
এই খাতের উন্নতি করতে পারলে আমাদের পর্যটনখাতেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। ২৩৫৫জন দেশীয় জাহাজে এবং ৫৪৩৮ জন বিদেশী জাহাজে চাকুরীত আছেন। নৌ-কর্মকর্তা এবং নাবিকদের বেতন বাবদ দেশে বৎসরে প্রায় ২হাজার ৪শত তিয়াত্তুর কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। অভ্যন্তরীণ জাহাজে রিভারসিবল গিয়ার সংযোজন করে দুর্ঘটনা হ্রাস করা হয়েছে। নৌ-পরিবহন খাতে আমাদের সেবার মান নিশ্চিৎ করতে পারলে অভ্যন্তরীণ আয় আরও বৃদ্ধি পাবে এবং অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌযানের সংখ্য্যা ১২৯৫৯টি। অভ্যন্তরীণ নৌ খাতে গত ৫বছরে নীট আয় করেছে ৫হাজার ১শ ছয় কোটি টাকার উপরে। বৈদেশিক পণ্য আমদানি কিংবা দেশিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে চট্টগ্রামে ও মংলা সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অভ্যন্তরীণ নৌপথ এখনও প্রধান মাধ্যম। সারা দেশে জ¦ালানি তেল পরিবহনের ক্ষেত্রেও প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় নৌপথ।
আমাদের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রও অভ্যন্তরীণ নৌপথকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের এ যুগে গোটা বিশ^ যখন একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের বহুমুখি পথ খুঁজছে, তখন বাংলাদেশের অমিত সম্ভাবনার এক উর্বর ক্ষেত্র বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও নৌ-পরিবহন খাত অনাদর, অবহেলা ও চরম উদাসীনতার শিকার। বহুজাতিক অটোমোবাইল কোম্পানিগুলোর ব্যবসা সম্প্রসারনের স্বার্থে তাদের পৃষ্ঠপোষক বিশ^ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কুপরামর্শ, রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা এবং দুর্বৃত্তায়নের কবলে পড়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের অনাগ্রহের কারণে নদী এবং নৌ চলাচল ব্যবস্থাসহ সামগ্রিক নৌখাত বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে।
একদিকে বছরের পর বছর ধরে পলি জমে ও মারাত্মক দূষণে নদীগুলো স্রোতহারা হয়ে নৌপথের আয়তন আশংকাজনক হারে কমছে। অন্যদিকে অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন,পরিবেশবিনাশী প্রকল্প প্রণয়ন এবং নদীখেখো ও ভূমিদস্যুদের করালগ্রাসে অনেক নদী বিলীন হয়ে গেছে। আমাদের নৌপথে এখনো বিদেশী কোন বিনিয়োগকারী নাই এবং এই নৌপথ এখনো দেশের অন্যতম অভ্যন্তরীণ আয়ের অন্যতম উৎস হতে পারে। এখানে আমাদেরকে অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হয় না। এতো প্রতিকূলতার মধ্যে আশার কথা যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও জাতীয় অর্থনীতি থেকে নৌ-পরিবহন খাত এখনো হারিয়ে যায়নি। চলতি শতকের প্রথমদিকে বিশ^ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল ব্যবস্থার ওপর এখনও বাংলাদেশের ৩০লাখ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। অভ্যন্তরীণ নৌপথে এখনও নিয়মিত ৩০শতাংশ যাত্রী চলাচল করে আর ২০শতাংশ পণ্য পরিবহন হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে গত দেড় দশকে নৌপরিবহন খাতের ওপর নির্ভরশীলতা আরো বেড়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সড়কখাতের তুলনায় নৌখাত আনুপাতিকহারে সরকারি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নদ-নদী প্রকৃতির দান। তাই নৌপথ তৈরিতে আবাদি কিংবা বসতি জমি অথবা কোন স্থাপনা ধ্বংস করতে হয় না। নৌপথে যাতায়ত আরামদায়ক,ব্যয়সাশ্রয়ী ও পরিবেশেবন্ধব। দূর্ঘটনার ঝুঁকিও তুলনামূলক কম।
পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও সড়কপথের তুলনায় নৌপথে ব্যয় আরো কম। বৈদেশিক পণ্য আমদানি এবং দেশিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অভ্যন্তরীণ নৌপথ এখনও প্রধান মাধ্যম। সারা দেশে জ¦ালানিতেল পরিবহনের ক্ষেত্রেও প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় নৌপথ। আর এই যোগাযোগের সহজতর মাধ্যমকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র শর্থ হচ্ছে নদ-নদী রক্ষা ও নৌ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন। নদী রক্ষা না হলে নৌ পথ বিলুপ্ত হবে, নৌ চলাচল ব্যববস্থা মুখ থুবরে পড়বে, প্রাকৃতিক মৎস্য আহরণ কমে গিয়ে জেলে মৎসজীবী সম্প্রদায় এবং নৌযানের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে মাঝি-মাল্লারা বেকার হবে। এর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়বে গ্রামীণ অর্থনীতিতে। যার আঘাত জাতীয় অর্থনীতিকেও ক্ষতিগ্রস্থ করবে। এসব প্রতিকূলতা মোকাবিলার জন্য নৌ খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন অপরিহার্য। নৌ-পরিবহন খাতে সোনালী অতীত হারালেও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও সুযোগ একেবারে হাতছাড়া হয়ে যায়নি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ২০১৮-১৯অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন নৌরুটে ৩ কোটি ৪৫লাখ ৩০ হাজার যাত্রী চলাচল করছে এবং এ থেকে আয় ৩হাজার ১৪৫কোটি ৩লাখ টাকা। তাছাড়া৫৪৮৩৫ লাখ টন পণ্য পরিবহন করা হয়ছে। যা গত ১০ বছর আগেও ছিল এর এক-তৃতীয়াংশ কম। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রতিবছর যাত্রী সংখ্যা এবং পরিবহনের পরিমাণ বেড়েই চলছে।
বাজেটে সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে রেলপথ এবং নৌপথকে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে রেলপথ এবং নৌপথ, দুটি ক্ষেত্রেই। অথচ আামরা জানি, নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীপথেই বেশিরভাগ মানুষ চলাচল করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ধারণা, সড়ক পরিবহনের সঙ্গে জড়িত প্রভাবশালী বক্তিদের কারণেই হয়তোবা রেলপথ এবং নৌপথ এভাবে যুগের পর যুগ গুরুত্বহীন এবং অবহেলিত থাকার অন্যতম প্রধান কারণ। এ কথা বলার অঈেক্ষা রাখে না যে, ভৌগলিক সুবিধার কারণেও আমাদের দেশের প্রায় সব নদ-নদীই পণ্য পরিবহন এবং যাত্রীবাহী জলযান চলাচল করার উপযোগী কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এদিকটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে চিরদিন অবহেলিত থেকে গেছে। আমরা সবাই জানি, পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও সড়ক পথের চেয়ে রেল ও নৌপথ অনেক বেশি সাশ্রয়ী। এর পাশাপাশি আর যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হলো সড়ক দুর্ঘটনা এখন অর্থাৎ এই সময়ে শুধু নয়, বিগত বেশ কযেক বছর ধরে রীতিমতো আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। এমন কোন দিন নেই, যেদিন দেশের কোথাও না কোথাও দু-চারটা সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে না এবং তাতে হতাহতের সংখ্যাও আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে তুলনায় রেলপথ এবং নদীপথে চলাচল যাত্রীদের জন্য অনেক নিরাপদ।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের নৌপথের দৈর্ঘ্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ। কারণ যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সড়ক ও রেলপথের চেয়ে নৌপথ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে যাই বলি যেভাবেই বলি আর যেভাবেই চিন্তা করি না কেন নৌপথ যাত্রীপরিবহন এবং পণ্য পরিবহনে অনেক নিরাপদ, অনেক সাশ্রয়ী, অনেক আরামদায়ক। দেশের চাহিদা বিবেচনা করে একে আরও বেশি গতিশীল করা এখন সময়ের দাবী। নদী ও নৌপথ সচল এবং পুনরুদ্ধার, নৌ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পর্যটন শিল্প বিকাশে নেওয়া পদক্ষেপ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কোন অঞ্চলে কোন কোন সমস্যা সমস্যা সেটি চিহ্নিত করে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নদীর গতিপ্রকৃতি অব্যাহত রাখতে পারবো। নদীর গতিপথ বজায় রাখতে পারলে, নদীর পাড় সংরক্ষণ করা গেলে স্বাভাবিকভাবেই পর্যটনও গতি পাবে।
বাজেটে বরাদ্ধ বৃদ্ধি করে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে । লঞ্চ টার্মিনালগুলো ঘাট শ্রমিকদের যে টর্সার তা বন্ধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যাত্রীদের সাথে এদের প্রায়শ হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এদের টর্সারের কারণে অনেক যাত্রীই নৌপথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। টার্মিনালগুলোতে যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে। ভ্রাম্যমান নৌ আদালত কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করা। নৌ দূর্ঘটনার সঠিক তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের আওতাভুক্ত অঞ্চলে বিপদগ্রস্থ জাহাজ উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা। জলদস্যূ এবং অবৈধ কার্যক্রম রোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নৌযানের সার্ভে এবং রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে।
কুতুবদিয়া , কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন বাতঘর পরিচালনার মাধ্যমে নৌযান সমূহকে দিক নির্দেশনা প্রদান ও রাজস্ব আদায় করা। আইএসপিএস কোড বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা। নৌ দিবস উদযাপনের মাধ্যমে সচেতনা তৈরি করা। নৌকর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পর্যপ্ত সুযোগ সুবিধা বরাদ্ধ করা। অভ্যন্তরীণ নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে নৌ পথে চলাচলকারী নৌযানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে কাগজপত্র সরজমিনে পরীক্ষা করা এবং এতদ্সংক্রান্ত বিধি লংঘনকরীদের বিরুদ্ধে মেরিন কোর্টে মামলা দায়ের করা, সংশ্লিষ্ট এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচলনায় সহায়তা প্রদান পরিদর্শনালয়ের মুখ্য দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই খাতের সকল দুর্নীতি রোধ করতে হবে। আমাদের চলাচলের জন্য যে কোন মূল্যে নদীপথকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নদীকে বাঁচাতে না পারলে আমরাও বাঁচতে পারবো না। প্রকৃতিও প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠবে। ফলে বৃদ্ধি পাবে, খড়া, বন্যাসহ নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নদী বাঁচাতে পারলে দেশ বাঁচবে। নদী আমাদের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা, অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস, বাণিজ্য সুবিধা, মৎস্য সমস্পদ, পর্যটন শিল্প আর আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায়। তাই অমিত সম্ভাবনা আমাদের নদীপথকে বাঁচাতে হবে যে কোন মূল্যে।
|
|
|
|

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় উপনিবেশিক বাংলায় রেলওয়ে স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে ইংল্যান্ডে চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা হতে থাকে। এরূপ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও কৌশলগত সুবিধাদিসহ বাণিজ্যিক স্বার্থ বিবেচনা। রেলওয়ে উনিশ শতকে প্রবর্তিত হয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক বিপ্লবের সূচনা করে। ভারতের ভাইসরয় লর্ড ডালহৌসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের কাছে ভারতবর্ষে রেলওয়ে স্থাপন কাজ শুরু করার জন্য অনেকগুলো প্রস্তাব পাঠান।
তবে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেতে ও সরকারের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনে বেশ কয়েক বছর লেগে যায়। ইতোমধ্যে, ১৮৫০ সালে গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে নামক কোম্পানি মুম্বাই থেকে ৩৩ কিমি দীর্ঘ রেললাইন স্থাপন করতে থাকে। এটিই ছিল ব্রিটিশ ভারতে রেলওয়ের প্রথম যাত্রা। বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে রেললাইন স্থাপনের কাজ শুরু করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ব্রিটিশ আমলেই বিবেচনা করা হয়েছিল। ১৮৫২ সালে গঙ্গা নদীর পূর্বতীর ধরে সুন্দরবন হয়ে ঢাকা পর্যন্ত রেললাইন বসানোর প্রস্তাব দেয়া হয়।
বিশ্বজুড়ে পাটের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য প্রধান পাট উৎপাদনকারী এলাকা ঢাকা এবং ময়মনসিংহ থেকে কলকাতা বন্দরে পাট সরবরাহ করার জন্য উন্নতমানের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮৮৫ সালে মূলত কাঁচা পাট নদীপথে কলকাতায় আনার জন্য ঢাকা স্টেট রেলওয়ে নামে খ্যাত ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা হয়ে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ১৪৪ কিমি দীর্ঘ মিটারগেজ রেললাইন স্থাপন করা হয়। ক্রমান্বয়ে এটিকে ময়মনসিংহ থেকে জামালপুর হয়ে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট এবং পরবর্তীকালে বাহাদুরাবাদ ঘাট পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।
১৯১৪ সালে পদ্মার উপরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ প্রকল্প বাস্তবায়ন উপলক্ষে শান্তাহার পর্যন্ত মিটারগেজ লাইনকে ব্রডগেজ লাইনে রূপান্তর করা হয়। ১৯১৫ সালের ৪ মার্চ দুই লেনবিশিষ্ট হার্ডিঞ্জ ব্রিজ রেল চলাচলের জন্য উদ্বোধন করা হয়। ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রামের সরাসরি যোগাযোগের জন্য ১৯৩৭ সালে ৬ ডিসেম্বর মেঘনা নদীর উপর রেলসেতু উদ্বোধন করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্তির পর পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান উত্তরাধিকারসূত্রে পায় ২,৬০৬.৫৯ কিমি রেললাইন এবং তা ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে নামে পরিচিত হয়। ১৯৬১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি এর নতুন নামকরণ হয় পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে। ব্রডগেজ রেল ইঞ্জিন বা ব্রডগেজ রেললাইনের উপরে চলাচল করার উপযুক্ত রেলযানসমূহ মেরামত করার কোন কারখানা পূর্ব পাকিস্তানে ছিল না।
তবে, পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে সৈয়দপুরে একটি মিটারগেজ রেল কারখানা পেয়েছিল। রেল পরিচালনার ক্ষেত্রে কতগুলো মারাত্মক অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তখন, যেমন, সংযোগবিহীন রেললাইন, যানান্তরকরণের অসুবিধা, যমুনা নদীর দুই ধারে নাব্যতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফেরিঘাটসংলগ্ন রেললাইনের নিত্য স্থানান্তর সমস্যা ইত্যাদি। উপরন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেললাইনের উপর দিয়ে প্রবল ধকল যায়। দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত সেগুলো সঠিকভাবে মেরামত করা সম্ভব হয়নি।
দেশ বিভাগের পরপরই সঙ্গত কারণে সৈয়দপুর কারখানায় ব্রডগেজ রেল ইঞ্জিন ও যানবাহন মেরামতের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশের পর এদেশের রেলওয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ রেলওয়ে, যা উত্তরাধিকারসূত্রে পায় ২,৮৫৮.৭৩ কিমি রেলপথ ও ৪৬৬টি স্টেশন। স্বাধীনতা যুদ্ধে রেলওয়ে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ফলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে অনেক বছরে সেগুলো মেরামত করতে হয়।
১৯৯৪ সালে যমুনা বহুমুখী সেতুর কাজ শুরু হয়। চার লেন সড়কপথ ও এক লেন ডুয়েলগেজ রেলপথবিশিষ্ট এই সেতুর উপরে আছে বৈদ্যুতিক সংযোগ, গ্যাস লাইন ও টেলিফোন লাইনের বন্দোবস্ত। ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন সেতু উদ্বোধন করা হয়। রেলওয়ে গেজ পদ্ধতিকে সুসঙ্গত করার জন্য যমুনা সেতুর পূর্ব প্রান্ত থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ১১৫ কিমি ডুয়েলগেজ লাইন নির্মিত হয় এবং জয়দেবপুর থেকে ঢাকা পর্যন্ত ৩৫ কিমি লাইনকে ব্রডগেজে রূপান্তর করা হয়। ২৪৫ কিমি দৈর্ঘ্য পার্বতীপুর-ঈশ্বরদী-জামতৈল ব্রডগেজ রেলপথ যমুনা সেতুর পশ্চিম প্রান্তে মিলেছে।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রেলওয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে কিছু মৌলিক পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়ে। সেই অনুসারে ১৯৭৩ সালে রেলওয়ে কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৬ ও ১৯৮২ সালে মার্শাল ল’ অর্ডিন্যান্স, এবং ১৯৯৫ সালে সরকারি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে রেলওয়ের উঁচু পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আবারও অনেক পরিবর্তন সাধন করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমানে সরকারি সংস্থা হিসেবে সরকারি সহায়তায় এবং ব্যবস্থাপনায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ১ জুলাই ২০০০ সালে বাংলাদেশে মোট ২,৭৬৮ কিমি রেললাইন ছিল, তার মধ্যে পশ্চিম জোনে ৯৩৬ কিমি ব্রডগেজ, ৫৫৩ কিমি মিটারগেজ এবং পূর্ব জোনে ১,২৭৯ কিমি মিটারগেজ।
নিরাপদ ও সুসংহতভাবে রেল পরিচালনা করা এবং লাইনের পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সমগ্র রেল ব্যবস্থাপনায় যথাযথ সাংকেতিক ব্যবস্থা ও টেলিযোগাযোগের বিন্যাস করা হয়। নিরাপত্তা আরও জোরদার করার জন্য Absolute Block Working System অনুযায়ী রেলওয়ের পরিবহণ ব্যবস্থা চালিত হয়। ১৯৯৫-৯৭ সালে ময়মনসিংহ-জামালপুর লাইনের ৬টি স্টেশনে এই ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৮০-৮৫ সালে ৩টি বড় বড় ব্রডগেজ স্টেশনে একই ব্যবস্থা চালু হয়। পার্বতীপুর-ঈশ্বরদী-খুলনা ব্রডগেজ লাইনে দ্রুতগতিতে ঘণ্টায় ৯৫ কিমি বেগে ট্রেন চলাচল করে। অন্যান্য স্টেশনগুলোতে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক সাংকেতিক ব্যবস্থাপনায় রেল পরিবহণ পরিচালনা করা হয়।
বাংলাদেশের অন্যান্য যানবাহনের তুলনায় রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল। ১৯৯৯ জুলাই থেকে জুন ২০০০ সালের মধ্যে মোট ৪৫৬টি রেল দুর্ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে ৬টি হয় মুখোমুখি সংঘর্ষে, ৪০৫টি সংঘটিত হয় লাইনচ্যুত হয়ে, ১টি অগ্নিকান্ডে, ৪৪টি অন্যান্য কারণে। এইসব দুর্ঘটনায় ২০ জনের মৃত্যু হয়, আহত হয় ২৩৩ জন এবং আর্থিক মূল্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪৫.৫০ লক্ষ টাকা। রেল পরিচালনায় দক্ষতা এবং নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রায় ৩০০ রেলস্টেশনের সঙ্গে ২,৭৬৮ কিমি-এর মধ্যে ১,৮০০ কিমি রেলপথের ওপর সর্বাধুনিক সমন্বিত অপটিক্যাল ফাইবার টেলিযোগাযোগ স্থাপন করা হয়।
এই ব্যবস্থায় ৩০টি ড্রপ ইনসার্ট এবং মাল্টিপ্লেক্সিং স্টেশন আছে। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সার্বিক পরিদর্শনের জন্য ১৮৯০ সালে প্রণীত রেলওয়ে অ্যাক্ট এবং পরবর্তী আদেশানুক্রমে সরকারি রেলওয়ে পরিদর্শককে রেললাইনের উপর দিয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের যোগ্যতা, রেললাইন, সেতু, সিগন্যাল ও রোলিং স্টকসমূহের উপযুক্ততা, বিশেষ দুর্ঘটনার তদন্ত করা এবং আরও অনেক আনুষঙ্গিক কাজ পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৮৪-৮৫ সালের শেষদিকে সমস্ত বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন বাতিল ঘোষণা করা হয়। রেল ইঞ্জিন দুই ধরনের, যথা- ডিজেল ইলেক্ট্রিক ও হাইড্রো ইলেক্ট্রিক। যাত্রী যানবাহনে বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির মিড-অন-জেনারেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়।
বাংলাদেশ রেলওয়ের আছে ৬টি কারখানা: ১টি সৈয়দপুরে, ২টি পাহাড়তলীতে, ২টি পার্বতীপুরে ও ১টি ঢাকায়। সবচেয়ে বড় কারখানা সৈয়দপুরে। এখানে উভয়প্রকার গেজের রেলকোচ এবং ওয়াগনের বড় ধরনের মেরামতের কাজসহ নতুন রেলকোচ ও ওয়াগন সন্নিবেশ করা হয়। পাহাড়তলীতে দুটি কারখানার মধ্যে ১টিতে সম্পন্ন হয় মিটারগেজ রেলযান ও ওয়াগন মেরামত ও সমাবেশ, অন্যটিতে মেরামত করা হয় মিটারগেজের ডিজেল ইলেকট্রিক রেল ইঞ্জিন। ১৯৯২ সালে পার্বতীপুরে ক্রমবর্ধমান ডিজেল রেল ইঞ্জিনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ১টি কেন্দ্রীয় ডিজেল কারখানা স্থাপন করা হয়। এটি হচ্ছে ইঞ্জিনের সব ধরনের বড় মেরামত এবং ওভারহলিং-এর প্রধান ও আধুনিক কারখানা। পার্বতীপুরে অন্য আরেকটি কারখানায় ব্রডগেজ ডিজেল রেল ইঞ্জিনের সাধারণ মেরামতের কাজ চলে এবং ঢাকা ওয়ার্কশপে মিটারগেজ রেল ইঞ্জিনের সাধারণ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।
তুলনামূলকভাবে দ্রুত ও উত্তম সার্ভিসের জন্য, গুদাম থেকে গুদামে সহজে যাতায়াতের কারণে মালামাল পরিবহণে রেলপথের চেয়ে সড়কপথই বেশি প্রাধান্য পায়। মূল্যবান মালামাল বহনের জন্য রেলওয়েকে খুব কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া গড়ে না ওঠার কারণে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মালবাহী রেলগাড়িগুলোর যাতায়াত একমুখী হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালবাহী গাড়ি গন্তব্যস্থলে মালামাল খালাস করার পর খালি ফিরে আসে। অপরদিকে, জাতীয় পরিবহণ মাধ্যমের অঙ্গ হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে অপরিহার্য দ্রব্যাদি, যেমন খাদ্যশস্য, সার, পাট, সিমেন্ট, কয়লা, লোহা, ইস্পাত, পাথর, পেট্র্রোলিয়াম, লবণ, চিনি ইত্যাদি স্বল্পমূল্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে হয়।
বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল কর্মকর্তা এবং পরিচালনাকারী স্টাফকে চট্টগ্রামে অবস্থিত রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী থেকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। রেলওয়ে খাতে বর্তমানের সংস্কার প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক সেবা বেসরকারীকরণের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। এর ফলে রেলওয়ের অধিকতর আর্থিক স্বয়ংনির্ভরতা অর্জন সম্ভব হবে। সংস্কার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে আছে উন্নততর প্রযুক্তি সংযোজন, নতুন রেললাইন স্থাপন, কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করা, লোকসানি শাখা লাইনসমূহ বন্ধ করন এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন জমির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা।
লেখক:
মো: আরাফাত রহমান
সহকারি কর্মকর্তা, ক্যারিয়ার এন্ড প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস বিভাগ,
সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়।
|
|
|
|

মার্ক জাকারবার্গ ২০০৪ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি ফেসবুক আবিষ্কার করেন। আর বাংলাদেশে ফেসবুক চালু হয় ২০০৬ সালে ২২ আগস্ট। প্রায় ১৬ বছর ধরে আমরা ফেসবুক জগতে এসেছি। সেই সূত্রে রেডমিক কিবোর্ড ইউজ করি। কিন্তু অনেকেই বাংলা টাইপিং করতে পারে না। একে তো টাইপিং করতে পারে না, আবার অন্যরা বাংলা টাইপিং করলে ব্যঙ্গ চোখে দেখে। মন থেকে এটি মেনে নিতে পারে না। আনস্মার্ট, গেয়ো, খ্যাত ভাবে। হয়তো অনেকেই মুখে বলে না। কিন্তু আচার আচরণে বোঝা যায়। এ যুগের ছেলেমেয়েরা বাংলিশ টাইপিংকে স্মার্ট বলে থাকে। এটাই নাকি আধুনিক, যুগের সঙ্গে মানানসই। কিন্তু বাংলিশ অনেকেই বুঝে না, গুরুত্বপূর্ণ কথা বাংলিশ এ লিখলে বোঝা যায় না। কিন্তু বাংলায় লিখলে একটি অক্ষর ভুল হওয়া সাপেক্ষেও সুন্দরভাবে বোঝা যায়। বাংলা টাইপিং এ যে টান থাকে তা বাংলিশে নেই। সাময়িকভাবে লেখা দ্রুত হলেও খাপছাড়া একটা ভাব থাকে। অনেকই ইচ্ছে করে বাংলা টাইপিং করে না। অনীহা দেখায় বাংলা টাইপিংয়ে। একটা গা-ছাড়া ভাব। মনে করে বাংলিশই সুপারস্টার। কিন্তু সে যে একটা ভুলের মধ্যে আছে সেটা কখনো অনুধাবন করে না।
বর্তমানে বাংলাদেশে ফেসবুক ব্যবহারকারী প্রায় ৪.৮ কোটি। প্রতি ৩ জনের ১ জন ফেসবুক ব্যবহার করে এই দেশে। এখন প্রশ্ন হলো- কতজন মানুষ বাংলা টাইপিং করে? কত জন মানুষ বাংলা টাইপিংয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে? অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে উত্তর আসবে অর্ধেক মানুষও বাংলা টাইপিং করে না। বেশির ভাগ মানুষ বাংলিশ টাইপিং করে। তাহলে কি বাংলা এতটাই সস্তা হয়ে গেল। তাহলে কি এতটা আত্মত্যাগ- মহিমা বিসর্জন মূল্যহীন হয়ে পড়লো।
আবার দেখি অনেকে মেসেঞ্জারে অভ্রতে লিখে। কেন? সরাসরি আমরা প্রভাতে লিখতে পারি না? বাংলাকে আমরা মন থেকে ভালবাসি, কোনো ফাঁক ফোকর রেখে ভালবাসলে ভাষার ভালবাসা পূর্ণতা পায় না। আর বাংলা তো মায়ের ভাষা। যে ভাষায় সাদা কাগজে কালো কলমে লিখতে কার্পণ্য আসে না, সে ভাষায় টাইপিংয়ে কি সমস্যা? আমরা বাংলা লিখতে পছন্দ করি কিন্তু কেন বাংলা টাইপিং করতে পছন্দ করি না? বাংলা টাইপিং কি মায়ের ভাষার সম্মান বাড়ায় না? বাংলা টাইপিং কি বাংলা ভাষাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় না? বাংলা টাইপিং কি শহীদের মর্যাদা বাড়ায় না? কেন আমরা পাশ্চাত্যের লোভে পড়ে বাংলা টাইপিংকে আনস্মার্ট ভাবছি? কেন মনে হচ্ছে বাংলা টাইপিং কঠিন, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার? কেন আমরা ১৬ বছরে বাংলা টাইপিং শিখলাম না? কেন আমরা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধে বাংলা টাইপিংয়ে অনীহা করি? প্রশ্ন কিন্তু রয়েই যায়। যার উত্তর পাওয়া খুবই মুশকিল। প্রথমদিকে বাংলা টাইপিং একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। কিন্তু কয়েকদিনের মাথায় সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। তারপর যে শ্বাশত অনুভূতি হয় তা বলে বোঝানো যাবে না। তখন নিজে থেকেই বাংলা টাইপিং কেউ ছাড়বে না। অনেকেই ইংরেজি বা বাংলিশে প্রশ্ন করলেও ইচ্ছে হবে না বাংলিশে উত্তর দিই। মনে হবে বাংলায় উত্তর দিই। তখন বাংলার প্রতি মহত্ত্ব বেড়ে যাবে আরো একধাপ। এ ধাপ মায়ের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগায়।
আবার দেখি অনেকেই লিখে ইউ কেমন আছো? এটা কোন ভাষা, আবার তো বুঝে আসে না। আধুনিক মানে এই নয় ভাষাকে মিশ্র করা। নিজের মতো ভাষাকে বিকৃত করে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করবো। ভাষার মান কমানো।
মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা- তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালবাসা। একজন বাঙালির জন্য বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারা কতটা সৌভাগ্যজনক তা সে নিজেও জানে না। হয়তো এর কোনো সীমানা নেই। এর পরিসীমা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলা ভাষায় যে শাশ্বত অনুভূতি আছে, তা পৃথিবীর কোথাও নেই। জোর করে সবই সম্ভব কিন্তু ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। বাংলাভাষাকে রক্ষা করার জন্য বাংলার সাহসী সৈনিকরা জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধ করতে হয়েছে, মায়ের ভাষার সম্মান রক্ষা করা জন্য। শুধু কি এই নয় মাস, তার আগে কত বৈষম্য গঞ্জনা ব্যঞ্জনার কটুক্তির শিকার হতে হয়েছে। অবশেষে আমরা পেয়েছি নিজের মায়ের বাংলাভাষা।
এখনো চোখ বন্ধ করে ১৯৭১ সালের কথা চিন্তা করলেই চোখে ভেসে আসবে লাশের পর লাশ। লাল রংয়ে ছেঁয়ে যাওয়া নদী। তাদের অকালে জীবন গিয়েছিল শুধুমাত্র একটি ভাষার জন্য। শুধুমাত্র মায়ের ভাষার সতীত্ব রক্ষার জন্য। সেই বাংলাভাষাকে কি আমরা অবজ্ঞা করতে পারি?
আধুনিকের চাকচিক্যের বাহুল্যতা বন্ধ না করলে আমরা বাংলা ভাষার ত্যাগের মহিমা কিভাবে বুঝবো? বাংলা টাইপিং একটা দেশপ্রেম। যে দেশপ্রেমে রয়েছে মনের গভীর আত্মতৃপ্তি। যে আত্মতৃপ্তি পেতে হলে মন থেকে বাংলা টাইপিংয়ের মহত্ত্ব বুঝতে হবে। বাংলা টাইপিং বাঙালি মননে সঞ্চারিত বাংলাভাষার ভালবাসার স্পন্দন। যারা বাংলাকে ভালোবাসে তারা কখনো বাংলিশ টাইপিং করে না। আমাদের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। মানবিকতার বিকাশে মন থেকে ভাষাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। আসুন আমরা বাংলা টাইপিং করি ও অন্যদেরকে এবিষয়ে উৎসাহিত করি।
মাহমুদা টুম্পা
শিক্ষার্থী
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
|
|
|
|

মাহমুদুল হক আনসারী
আত্মহত্যা একটি মারাত্মক রোগ। মানুষ নানা ভাবে একজন রোগী। মানসিক, শারীরিক রোগছাড়া খুব কম মানুষই পৃথিবীতে আছে। মানুষ আল্লাহর প্রেরীত প্রতিনিধি। সব সৃষ্টির উপর মানুষ শ্রেষ্ট সৃষ্টি। মানুষের বিবেক বুদ্ধি আছে। চিন্তা চেতনা ভালো মন্দের মাপকাটি আছে। কোনটি সত্য আর কোনটি অসত্য সেটি মানুষ বুঝবার ক্ষমতা রাখে। মানুষ একাকি ভাবে জীবনে চলতে পারে না। মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে আগমন সেটিও অন্যের উপরে নির্ভরতা ও অপরের সাহায্য। আসার পর থেকে পিতা মাতা, অপরাপর পরিবারের সদস্যদের সাহায্য তার বেডে উঠা। ক্রমেই একজন শিশু থেকে সে বড় হতে থাকে। হাটি হাটি পা পা করে সেই শিশু বড় হয়ে উঠে। সে কথা বলতে শিখে।
অক্ষর জ্ঞান অর্জন শুরু করে। বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা শুরু হয়। ভাষা, বই, সংস্কৃতি, শিখতে থাকে। পরিবার সমাজ, রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে। মানুষ চিনা শুরু হয়। ধীরে ধীরে বড় হয়। লেখা পড়া স্কুল, কলেজ, বিশ^বিদ্যালয়, পর্যন্ত তার যাত্রা চলতে থাকে। সে একজন মানুষ হিসেবে সমাজের বিভিন্ন দিক ও সৃষ্টি কালচার অনুসরন অনুকরনীয় হয়ে উঠে। সে কিন্তু যা শিখে তার পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র হতে শিখছে। আত্মীয় স্বজন বন্ধু মহল, সমাজের চতুপাশ^ হতে আহরণ করছে। যা দেখছে তাই শিখছে, তাই করার উপর অভ্যস্ত হচ্ছে। এটি সমাজের একটি চরিত্র। দেখেই অনুসরন অনুকরন। যত বড় হচ্ছে ততই তার চাওয়া পাওয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার চাহিদা আগ্রহ আবেদন নিবেদন বাড়ছে।
এটি মানুষের সভাবগত অভ্যাস। মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নেই । পাওয়ার কোনো কমতি নেই। আবেদনের শেষ নেই । যা পেয়েছে আরো পেতে চায়। যা পেয়েছে আরো অধিক ভালো মন্দ খাওয়ার পাওয়ার চাওয়ার আগ্রহ বাড়তে থাকে।
মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হিসেব আছে। একজন শিশুকে পিতা-মাতার নিকট দৈনন্দীন কর্মের ভালো মন্দ হিসেব দিতে হয়, কি করবে করবে না সেটির জন্য আবেদন করতে হয়। সব ধরনের মানুষকে জবাব দিহিতার মধ্যে চলতে হয়। জবাব দিহিতার বাইরে কেউ নয়। সন্তান-সন্তানাদির খবর রাখা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা সেটি কোনো দুষ ও ভূল বিষয় নয়। সন্তানের চলাচলে খবর রাখা দায়িত্বশীল পরিবারের কর্তৃব্য। সময় মতো সন্তানের সৎ সঠিক চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অভিভাবকের কর্তব্য। সেটিকে কোন সন্তান ভূল হিসেবে চিন্তা করলে সেটি হবে বাস্তব একটি কঠিন ভূল। সন্তানের প্রয়োজনীয় জীবন চলার উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অভিভাবক পরিবারের উপর ন্যস্ত থাকবে। ইচ্ছে করে ভালো মন্দ কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত সন্তান নেয়া উচিৎ নয়। সবকিছুর চিন্তা সিদ্ধান্ত অভিভাবক সুচিন্তিত ভাবে গ্রহণ করবেন নিজ সন্তানের জন্য।
বর্তমানে তথ্য প্রযোক্তির যোগ। প্রায় পরিবারে সন্তানদেরকে প্রযোক্তি নির্ভর মোবাইল দেয়া হয়েছে। সন্তান তার লেখা পড়ার সাথে সাথে মোবাইলের মাধ্যমে তার আশ পাশ চিনতে পারছে। জানতে পারছে, সকলের আচার আচরণ মানুষের চিন্তা ও চেতনা। রুচি অরোচি, দেখতে দেখতে একজন শিশু, কিশোর, যুবক, যুবতী, মানুষ অনেক কিছু সেখান থেকে শিখছে। এ শিখা থেকে মানুষ অভ্যাস পরিবর্তন করছে। চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে। ভাষা, কথা, আচার অনুষ্ঠান বদলে ফেলছে। মানুষ মূলতঃ কাকে অনুসরন করবে সেটি ঠিক ভাবে বুঝতে পারছেনা। কী কী অনুসরন করবে,কার কাছ থেকে আদর্শ শিখবে সেটি ঠিক করতে পারছেনা। চতুর্পাশে যা দেখছে তাই গ্রহণ করতে মন চায়। সামর্থ্য আমার কতোটুকু পর্যন্ত আছে সেটির হিসেব না করে ইচ্ছা ও চাহিদা বৃদ্ধি মূলত আত্মহনন ও আত্মহত্যা নামক অপসংস্কৃতির জন্ম। কোনো কিছু পাওয়ার জন্য আত্মহনন যোগ্যতা নয়। পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা মাধ্যম ও হতে পারে না। আত্মহত্যার প্রচলন কম বেশি পৃথিবীর সব দেশে আছে। আত্মহত্যার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো ধার্মিক ব্যাক্তি আত্মহত্যার পথ অনুসরণ করতে পারে না। কোনো মেধা সম্পন্ন মানুষ সে কাজ পছন্দ ও বাস্তবায়ন করতে পারে না।
এটি একটি জগন্য অপরাধ। ধর্ম ও রাষ্ট্রের মাপকাঠিতে আত্মহনন অসম্ভভ কঠিন গর্হিত কাজ । জীবন মৃত্যু সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ। এর বাইরে জীবন ও মৃত্যু হয় না। পূথিবীর সমস্ত অর্থ খরচ করে ও একটি জীবন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। ইচ্ছে করে মৃত্যুর যাত্রী হওয়া সৃষ্টিকর্তার সাথে চরম ভাবে বেয়াদবী ছাড়া কিছু নয়। এ অপরাধের বিচার ও শাস্তি খুবই কঠিন । এ মর্মান্তিক অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো পথ আছে বলে আমার জানা নেই। জীবন কোনো মানুষের জন্য সুখকর বিষয় নয়। জীবনে সর্বদা শান্তি সূখ মিলবে সেটিও ভাবা ঠিক নয়। মানব জীবন অর্থ সূখ শান্তি দু:খ বেদনার সংমিশ্রন। তাই জীবনে দু:খ অভাব অনটন সমস্যা লেগেই থাকবে সেঠিকে চরম ভাবে বিশ^াস করতে হবে। কঠিন ভাবে নিজের উপর অন্যায় সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। সফলতা ব্যর্থতা জীবনের সর্বদায় সঙ্গী। চাওয়া পাওয়ার আগ্রহ চাহিদা জীবনে থাকাটাই স্বাভাবিক। সফলতা আর ব্যর্থতা মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত জীবনে সম্পৃক্ত থাকবে। একজন সাধারণ মানুষ থেকে সর্বচ্চো ব্যাক্তি পর্যন্ত তার কোনো দিন চাহিদার শেষ থাকে না। এটিই জীবন এবং এটিই সত্য। এর বাইরে চিন্তা করার বাকী থাকে না।
কেন আত্মহত্যা করছে, কোন অভিমান ইচ্ছে পূরণ না হওয়ার কারণে এ পথ বেছেঁ ন্য়ো ইচ্ছে পূরণ করতে হলে পরিশ্রম ও সাধনা থাকতে হয়। শুধু শুধু কর্ম ও সাধনা হীন ভাবে কোনো আশা ইচ্ছে পূরণ হয় না। সেটিও সমাজকে বুঝতে হবে। যারা এ পথের যাত্রী হয়েছে, তারা কোথাও না কোথাও কর্ম কাজে সমাজ হতে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। সেটি সকলেই বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় । কিন্তু যিনি আত্মহত্যা করছেন তিনি ভূল কাজে পা বাড়িয়েছেন। সামর্থ্যরে বাইরে তার চাহিদা ছিল। চিন্তা বুদ্ধি কর্মসূচিতে অবশ্যই ভূল ছিল। তাই আত্মহত্যার পথ বেছেঁ নেয়। জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিলেই যে, তার মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে সেটা কিন্ত নয়। আত্মহননের মাধ্যমে একটি দুটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে , তা নয় । বরং রাষ্ট্র ও সমাজ অধিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবং হচ্ছে। প্রতিবাদের ভাষা এটি নয় আরও অনেক ধরনের ভাষা দিয়ে প্রতিবাদ করা যেতে পারে। এ ধরনের অভ্যাস হতে মানবসমাজকে বিরত থাকা চায়। এসব বিষয়ের প্রতি সমাজকে সচেতন হতে হবে। অধিক ভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সামাজিক আন্দোলন ও কাউন্সিলিং গড়ে তুলতে হবে।
কী পরিমাণে আত্মহনন হচ্ছে সেটির হিসেব দেয়া আমার লেখার উদ্দেশ্য নয়। সমাজকে এ চরিত্রের মারাত্মক ব্যাধি থেকে সচেতন করাই হলো লেখার মূল উদ্দেশ্য ।
করণীয়, শিশু বয়স থেকেই যার যার ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে সন্তানদের প্রতি মূল্য বোধ চর্চা করতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পারিবারিক সামাজিক ভাবে হতাশার অভ্যাস পরিহার করতে হবে। সামর্থ্যের বাইরে আবেদন নিবেদন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। লোভ লালসা পরিহার করতে হবে। উচ্চা বিলাসি জীবন যাপনে সন্তানদের অভ্যস্ত করা থেকে বিরত রাখতে হবে। সহজ সরল জীবন যাপনে চর্চা শিখাতে হবে স্বল্প ও মিতব্যায়ী শিক্ষা দিতে হবে। চারিত্রিক আদর্শ তৈরি করতে মহমনীষীদের জীবনী অনুসরণের উপর গুরুত্ব রাখতে হবে। সুশৃংখল জীবন যাপনে জীবনের শুরু থেকে অভ্যাস্ত করতে হবে। বখাটে, অসৎ চরিত্রহীন সঙ্গ হতে সতর্ক রাখতে হবে। জীবনের প্রথম থেকে একজন অভিভাবক তার সন্তানের প্রতি কঠোর দায়িত্ব শীল ভূমিকা পালন করলে হয়তো বা ব্যাক্তি , পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র আত্মহত্যার মতো মারাত্মক সামাজিক এ ব্যাধি থেকে রক্ষা পেতে পারে। আসুন আমরা আমাদের প্রিয় সন্তানদের প্রতি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে অভিভাবক সুলভ ভূমিকা পালন করি।
লেখক
মাহমুুদুল হক আনসারী
সংগঠক, গবেষক, কলামিষ্ট
|
|
|
|

বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। ২০১৮ সালের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যমতে, বাংলাদেশের শ্রমশক্তির ৪০.৬ ভাগ কৃষিনির্ভর। দেশের জিডিপিরর ১৪.১০ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে তিনগুণ। সার-কীটনাশকে ভুর্তকী প্রদান, নিয়মিত সরবরাহ, কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে চতুর্থ, ইলিশে প্রথম, সবজিতে তৃতীয়, আলুতে ষষ্ঠ, কাঁঠালে দ্বিতীয়, আমে অষ্টম, মিঠাপানির মাছে তৃতীয়, চা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দশম। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে চাল উৎপাদিত হয়েছে ৩ কোটি ৮৬ লাখ টন, আলু উৎপাদিত হয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ টন যেখানে দেশে আলুর চাহিদা রয়েছে ৮৫-৯০ লাখ টন, সবজি উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ৯৭ লাখ ১৮ হাজার মেট্রিক টন, ইলিশের উৎপাদন ছিল ৫ লাখ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন, আম উৎপাদন হয় ১ লাখ ৭৯ হাজার টন। বাংলাদেশে ৩৪ লাখ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন স্বাদু পানির মাছ উৎপাদিত হয়েছে, চা উৎপাদন হয়েছে ৯৬.৫১ মিলিয়ন কেজি।
কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণা ও যথাযথ তদারকির ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়লেও সে হারে বাড়েনি কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি আয়। কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ যতোটা এগিয়ে কৃষি বিপণনে ততোটা পিছিয়ে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত না করার কারণে কৃষকের উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের ৩০ শতাংশই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হিমাগারের অভাবে মৌসুমে ক্ষেতেই নষ্ট হয় অধিকাংশ সবজি। এছাড়া পরিবহন সমস্যার কারণে পণ্য সুষম যোগান সম্ভব হয়না। হিমাগারের অভাবে সস্তায় পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয় কৃষকরা। এ সুযোগ লুফে নেয় কিছু অসাধু মধ্যস্বত্বভোগী। তারা কৃত্রিম বাজার সংকট তৈরি করে ক্রেতাদের নিকট চড়া দামে কৃষিপণ্য বিক্রি করে। ফলে উভয়পক্ষই ক্ষতি সম্মুখীন হয়। এছাড়াও জাহাজ-বিমানের পরিবহন খরচ বৃদ্ধি, কন্টেইনার সংকটের কারণেও বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না রপ্তানি। রপ্তানির সুযোগ না থাকায় এবং হিমাগারের অভাবে প্রতিবছর মাঠেই নষ্ট হয় কয়েক লক্ষ টন আলু। দেশের আলুর উৎপাদন কোটি টনের উপরে হলেও রপ্তানি হয় ৪৫ হাজার টন মত। বিশ্ববাজারে আলুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রায় ৪০টি দেশের প্রধান খাদ্য তালিকায় আলু থাকলেও চেষ্টার অভাবে বড় একটি বাজার আমরা দখল করতে পারছিনা। এছাড়া আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ করে বিস্কুট, চিপসসহ নানান মুখরোচক খাবার তৈরি করা গেলেও দেশে গড়ে উঠেনি যথেষ্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান।
বাংলাদেশ সবজি উৎপাদনে অন্যান্য দেশের তুলনায় এগিয়ে থাকলে বাজার খুব সীমিত। দেশের কাচা সবজি রপ্তানির ৮০ শতাংশ আসে সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কাতার, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব ও কুয়েত এই ছয়টি দেশ থেকে। বাকী ২০ শতাংশ আসে ইতালি, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, সুইডেন, কানাডা, জার্মানির মতো অন্যান্য ৩৫টির বেশি দেশ থেকে।
মৎস উৎপাদনে শীর্ষে থেকেও রপ্তানিতে পিছিয়ে বাংলাদেশ। রপ্তানির সিংহভাগ আসে চিংড়ি থেকে। আন্তর্জাতিক বাজারে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের রয়েছ ব্যাপক চাহিদা। কিন্তু সে খাতটিও অন্যান্য দেশগুলোর দখলে। বাংলাদেশে এক সময় দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল চা। সময়ের পরিক্রমায় সেই চিত্র বদলে গেছে। গত দশবছরে চায়ের উৎপাদন বাড়লেও কমেছে রপ্তানি। এছাড়াও ইউরোপের দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে চা আমদানি করে তা প্যাকেটজাত করে চড়া দামে পুনঃরপ্তানী করে যার ফলে মুনাফার বড় একটি অংশ চলে যাচ্ছে তাদের হাতে। পাট একসময় দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য হলেও পাটজাতদ্রব্য আমরা বিশ্বের কাছে পরিচিত করাতে ব্যর্থ হওয়ার এ শিল্প এখন আর নেই বললেই চলে। দেশে আমের রপ্তানি কিছুটা বাড়লেও ব্র্যান্ডিং ও প্যাকেজিংয়ের অভাবে তাও তেমন আশানুরূপ নয়।
দেশ কৃষিক্ষেত্রে যেভাবে এগুচ্ছে সেভাবে যদি কৃষিপণ্যের বিপণন না হয় তবে কৃষক পণ্যের দাম পাবেনা যা কৃষিখাতে উন্নতির প্রধান অন্তরায়। দেশের শ্রমশক্তি কৃষিখাতের একটি প্লাস পয়েন্ট সাথে প্রযুক্তির সমন্বয় পারে দেশকে সমৃদ্ধ করতে। বিশ্ববাজারে দেশের কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ পারে দেশের বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করতে। তাই সার-কীটনাশক সরবরাহের পাশাপাশি কৃষিপণ্য বিপণনে বিশেষ মনযোগ দেয়া প্রয়োজন।
-মো. তাজুল ইসলাম
শিক্ষার্থীঃ- মার্কেটিং বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
|
|
|
|

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হলো দারিদ্র্য। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার এর পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত পরিভাষা। বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের বড় একটা অংশ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদের একমাত্র ভরসা বেসরকারি ঋণদাতা সংস্থা। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে কেউ উপকৃত হয়েছে কেউবা সব হারিয়ে সর্বশান্ত হয়েছে। তবে এনজিওগুলো পরিবারের স্বাস্থ্য, সন্তানের শিক্ষা, নিরাপদ পানি ও সৌচাগার ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। কিছু ভালো দিক থাকলেও এনজিও নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।
বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ফরহাদ মজহার বলেছেন, ‘ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্যবিমোচন করে না বরং সামন্ত সমাজের ভূমিদাসের মতো এ যুগের মানুষকে গ্রামীণ ব্যাংক এক ধরনের ঋণদাসে পরিণত করছে। মানুষের দারিদ্র্যতাকে কাজে লাগিয়ে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে লাভজনক ব্যবসা পরিচালনা করছে এসব ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওর ভূমিকা নিয়ে মিশ্র মতামত দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা, কেউ কেউ বলছেন কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে। আবার কেউ বলছেন ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। এ ঋণ দারিদ্র্য দূরীকরণে পুরোপুরি ব্যর্থ, এই ঋণ নিয়ে অনেকেই সর্বস্ব হারিয়েছেন; কেউ কেউ আবার ঋণের বোঝা সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। বাংলাদেশের হতদরিদ্র মানুষ ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে ৬৭শতাংশই ব্যায় করে অলাভজনক/ অনুৎপাদনশীল খাতে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক কোন ভূমিকাই পালন করে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ঊট) আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, হতদরিদ্র ব্যাক্তিদের (৫০-৭৫)শতাংশই ঋণগ্রস্থ। বেসরকারি সংস্থাগুলো মিথ্যা প্রলোভন ও স্বপ্ন দেখিয়ে দরিদ্র্য জনগণকে ঋণ নিতে আগ্রহী করে তুলে। কিন্তু গ্রাহকেরা ঋণের টাকা কোথায় খরছ করছে তার খবর রাখে না কেউই। অনেকে ঋণের টাকায় ধারদেনা শোধ করে, আসবাবপত্র কিনে, যৌতুক দেয়, ঘর মেরামত করে, আবার অনেকের স্বামী নেশা করে ঋণের টাকা নষ্ট করে ফেলে। যার ফলে কোন আয় তো নয়ই বরং আরও উচ্চ সুদের বেড়াজালে আটকা পড়ে সর্বশান্ত হয়ে পরছেন। গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার (২০-৪৪)শতাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্ষুদ্রঋণ যদি সফল হতো তবে আজও কেন ৭ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে ? দেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের সুচনা হয় আশির দশকে। ৪০বছর পর ও এমন কোন প্রমাণ নেই, যাতে মনে হতে পারে ক্ষুদ্রঋণ মানুষকে দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। তবে এই চিত্র আমরা দেখেছি যারা দারিদ্র্য বিমোচনে মাঠে নেমেছেন তারা শত শত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। ঋণ গ্রহীতারা ঋণকৃত টাকা কোন উৎপাদনশীল খাতে লাগাতে পারেনা যার ফলে আয় হয়না। আর আয় না হলে ঋণ পরিশোধ করবেই বা কিভাবে? আবার ঋণ গ্রহীতারা ঋণ গ্রহনের একমাস বা এক সপ্তাহ পরই কিস্তি শুরু হয়। এখন প্রশ্ন হলো ঋণকৃত টাকা তো মাত্রই বিনিয়োগ হলো লাভ আসতে সময় লাগবে। তাহলে এমতাবস্থায় কিস্তি কিভাবে পরিশোধ করবে? আবার সঞ্চয় এর কথা বলে এরা কিছু টাকা কেটে রেখে দেয় যা পরে ফেরত দিতে চায়না। ১০ হাজার টাকা ঋণ দিলে ঋণ উঠানোর সময় ৫০০ টাকা কেটে রাখে সঞ্চয় খাতে। কোন কোন এনজিও গ্রাহকের চাহিদা ছাড়াই বীজ, মুরগির বাচ্চা, গাছের চারা কিনতে বাধ্য করে। এতকিছু কাটার পর বাকি টাকা বেশির ভাগ সময়ই আয় বৃদ্ধি কার্যক্রমে সফল হয়না।শুধু ঋণের বোঝাই বেড়ে যায়। অনেক ঋণ গ্রহীতার শেষ পর্যন্ত ভিটেমাটি বিক্রি করেও ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি মেলেনা। কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় ঘরের টিন খুলে নিয়ে যায়, আসবাবপত্র বিক্রি করে দেয়, অপমান অপদস্ত করে এনজিও কর্মীরা যা সইতে না পেরে অনেকে আআত্নহত্যার পথ বেচে নেয়। দারিদ্র্যতার দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারী পুরুষেরা আশ্রয় নেয় এনজিওগুলোতে কিন্তু মুক্তি তো মেলে না। তাহলে এনজিওর সুফল কোথায়?
কিছু পরিবর্তন আনার মাধ্যমে হয়তো সুফল বয়ে আনা যেতে পারে, যেমন সুদের হার কমানো, উৎপাদন খাতে ব্যয় হচ্ছে কিনা তদারকি করা, নগদ টাকা না দিয়ে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সরঞ্জাম কিনে দেয়া এবং প্রশিক্ষণ দেয়া (মহিলাদের সেলাই মেশিন, পুরুষদের রিকশা, অটো ইত্যাদি), স্বল্পমেয়াদি ঋণকে দীর্ঘমেয়াদী করা। ক্ষুদ্রঋণ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে, তবে ক্ষুদ্রঋণ প্রক্রিয়ার ধরন, পরিধি ও ভারসাম্য বিষয়ে গবেষণা অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণ। ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে পরিবর্তন আনা দরকার নচেৎ এটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কোন কাজেই আসবে না।
লেখক: জান্নাতুল নাইম মিশি
শিক্ষার্থী, লোক প্রশাসন বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।
|
|
|
|

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ নতুন নয়। যুগ যুগ ধরে ডানপিটে ছেলে, মাস্তান, যারা এলাকায় হৈ-হুল্লোড়, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা থেকে শুরু করে মারামারির মতো ঘটনা ঘটাত তাদের কিশোর অপরাধী হিসেবেই সবাই জানত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের গতি, প্রকৃতি ও স্বভাবে এসেছে আরও নেতিবাচক পরিবর্তন। বিগত কয়েক দশকে দেশে কিশোর অপরাধের পরিসংখ্যানই বলছে আমাদের কিশোররা কীভাবে প্রচলিত আইন ও সামাজিক অনুশাসনের জাল ছিন্ন করে সাধারণ অপরাধ থেকে খুন, ধর্ষণসহ জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে এবং এর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের অপরাধের মাত্রা বয়স্ক অপরাধীদের নিষ্ঠুরতাকেও হার মানাচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিভিন্ন সময় তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে, তাদের সংশোধনের আওতায় নেওয়া হচ্ছে কিন্তু তাতে করে তাদের সংখ্যা ও অপরাধ কমছে না।
কিশোরদের অপরাধে জড়িয়ে পড়া বহুলাংশে নির্ভর করে সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম পরিবারের দায়িত্ববোধ বা দায়িত্বহীনতা। অতীতে আমাদের সমাজে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে কিশোরদের যে কোনো বিচ্যুত আচরণের বিচার বা সমাধান করা হতো। এখনও গ্রামাঞ্চলে, এমনকি শহরে দুর্বলভাবে হলেও সে রকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। তখন মানুষ বিচারের জন্য পুলিশ বা আদালতে না গিয়ে কিশোরদের অভিভাবক বা প্রয়োজন হলে সমাজপতিদের কাছে যেত এবং এভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কাজ করত। পরিবারগুলোও কোনো অভিযোগ পেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করত; যাতে তার কিশোরটি ভবিষ্যতে আর অপরাধে জড়িয়ে না যায়। তাই কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকার বিষয়টি ব্যাপক।
অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা যেমন কিশোরদের মনে দাগ কাটে, তেমনি প্রাচুর্যও। অভিভাবকদের ঠিক করতে হবে সন্তানদের প্রত্যাশার মাত্রা কতটুকু হওয়া উচিত। তাদের সব আবদার সহজে মেনে নেওয়ার মধ্যে তাদের মধ্যে যে সহজাত পাওয়ার ভাবনা তৈরি হয়, তা কি সব সময় ভালো? আবার তাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চাহিদা পূরণের দায় কিন্তু অভিভাবকদের। মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীর হাতে যদি দামি স্মার্টফোন দেওয়া হয় তাহলে এর ফল ভালো হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। বিদ্যালয়পড়ুয়া সন্তান কেন বিদ্যালয়ে বা নামাজে যাওয়ার সময় সঙ্গে মোবাইল নিয়ে যাবে? মোবাইল দিয়ে সন্তান কী করে, তা ক’জন অভিভাবক সচেতনভাবে তদারক করেন? অনুরূপভাবে সন্তানদের হাত খরচের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। সামর্থ আছে বলেই কিশোর সন্তানকে ইচ্ছেমতো টাকা দেওয়া পক্ষান্তরে তাদের বিপথগামী করা। বাড়তি টাকা দিয়ে সিগারেট বা মাদক সেবন যে করবে না সে নিশ্চয়তা কতটুকু?
আজকের ব্যস্ত নাগরিক জীবনে অভিভাবকরা সন্তানদের প্রয়োজনীয় সময় দিচ্ছেন কি না সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির এ যুগে সবাই নিজের ডিভাইস নিয়ে ব্যস্ত। একই ছাদের নিচে বাস করেও সবার জগৎ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যম ও ইউটিউবের ব্যবহার এত বেশি হচ্ছে, মা-বাবা নিজেরাই খেয়াল করছেন না যে তাদের সন্তানদের একাকিত্ব। ফলে তাদের মানসিকতা হচ্ছে ভিন্ন। এমনকি বিনোদনের সঠিক সুযোগ না থাকায় তাদের মধ্যে কিছু করার তাড়না তৈরি হয়; যা পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে বিচ্যুত ভাবনার জন্ম দিচ্ছে।
সন্তানটি কার সঙ্গে মিশছে বা রাতে কেন দেরি করে ফিরছে- তা দেখার দায়িত্ব কিন্তু পুলিশের নয়, মা-বাবার। সন্তানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করলে তা রোধ করা তাদের আবশ্যিক দায়িত্ব। কিন্তু কারও কারও ভাবনা ভিন্ন; মনে করেন ছেলেটা বড় হচ্ছে, একটু স্বাধীনতা দরকার। তা ঠিক, কিন্তু সেটার মাত্রাও দেখার বিষয়। অথচ এক সময় আসে যখন সে আর সীমার বাইরে চলে যায় আর অভিভাবকদের জন্য থাকে হাহাকার।
এ রকম অনেক দায়িত্ব আছে পরিবারের, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল হচ্ছে; ফলে কিশোররা হচ্ছে বিচ্যুত। তাই কিশোর অপরাধ রোধে পরিবারের ইতিবাচক ভূমিকা জোরালো না করলে আইন দিয়ে সেটা রোধ করা প্রায় অসম্ভব। এটা আমি মনে করি৷
লেখক: রেকসনা খাতুন
সার্জেন্ট, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ।
|
|
|
|

অটিজম কোন রোগ নয়। এটি মস্তিষ্কের বিকাশজনিত একটি সমস্যার নাম। গর্ভকালীন শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে প্রতিবন্ধকতার কারণে সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ বিকাশ বাধাগ্রস্ত হলে অটিজমের উদ্ভব হয়। এ সমস্যা যেসব শিশুদের মাঝে সৃষ্টি হয় তাদের আমরা প্রতিবন্ধী শিশু হিসেবে অভিহিত করি। আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধী শিশুরা অবহেলিত, নিগৃহীত। তাদেরকে রোগাক্রান্ত মনে করা হয় এমনকি কেউ কেউ তাদেরকে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক পিতা-মাতার কৃতকর্মের ফল হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। যা স্পষ্টতই ধর্মীয় গোঁড়ামির আওতাভুক্ত। এহেন অযৌক্তিক মনোভাব পরিহার করা উচিত। কেননা সৃষ্টিকর্তা তাঁর সকল সৃষ্টিকেই বিশেষ বিশেষ গুণে গুণান্বিত করে সৃষ্টি করেন। প্রতিবন্ধী শিশুরাও আমাদের সমাজের অংশ। তাই তাদেরকে হেয় করলে কিংবা আড়াল করে রাখলে চলবে না। বরং তারা কিভাবে আমাদের মতো স্বাভাবিক মানুষদের সাথে সাথে এগিয়ে যাবে তার জন্য জন্য আমাদের সহযোগীতার মনোভাব পোষণ করে তাদের পাশে থাকতে হবে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পিতা-মাতা, অভিভাবক এমনকি ব্যক্তিবিশেষে আমাদের বেশ কিছু করণীয় আছে। যেমন: প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে প্রকৃতির সাথে পরিচিত করতে হবে। প্রকৃতির সকল উপাদানের সাথে তাদের যেন পরিচয় হয়। তারা যেন প্রকৃতির সৌন্দর্য, রূপ, রস, গন্ধকে উপভোগ করতে পারে। যাতে তাদের মানসিকতায় প্রফুল্লতা জাগে। চিত্তবিনোদনের জন্য তাদেরকে বিনোদন পার্ক, দর্শনীয় স্থান, বিভিন্ন মেলা ও সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতে হবে। তারা যেন নিঃসঙ্গতা অনুভব না করে সেজন্য তাদেরকে নিয়মিত সঙ্গ দিতে হবে। তাদের পাশে থাকতে হবে। তাদেরকে সমাজের অন্যান্য শিশুদের সাথে মেশার সুযোগ করে দিতে হবে। এতে স্বাভাবিক শিশুদের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এতে তাদের বিকাশ সাধিত হবে। তাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। বিশেষত মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। নিয়মিত স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। তাদের সামনে ঐসব শিশুদের অস্বাভাবিকতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদেরকে সর্বদা হাসিখুশি রাখতে হবে। অভিভাবকদের ধৈর্য ধারণ করে তাদের লালনপালন করতে হবে। তাদের প্রতি নিজের রাগকে কাবু করতে হবে। তারা উত্তেজিত হলেও ঠাণ্ডা মাথায় তা নিয়ন্ত্রণ করাতে হবে। তাদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যাক পৃথক বিশেষায়িত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। পাশাপাশি তাদের জন্য চিত্তবিনোদনেরও ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন এসবে তাদের অংশগ্রহণ করাতে হবে। যাতে করে তারা এগিয়ে যাবার মানসিক ইন্ধন পায়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুর পরিবারের সদস্যদের মনে সাহয জোগাতে হবে তাদেরকে ধৈর্যশীল হতে প্রভাবিত করতে হবে। ঐসব শিশুদের খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য রাখতে হবে যাতে মানসিক বিকাশের সাথে সাথে তাদের শারীরিক বিকাশও ত্বরান্বিত হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন সম্পর্কে নিজেকে জানতে হবে এবং অন্য সবাইকে তা অবহিত করতে হবে। শিশু নির্যাতন বিশেষত প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ করতে আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। আমরা সামাজিক জীব। প্রতিবন্ধী শিশুরাও আমাদের সমাজের অংশ। কাজেই তাদের প্রতি আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমাদেরকে তাদের পাশে থাকতে হবে। তারাও যেন অন্য সব মানুষের মতো আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে অংশীদারিত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে, তাদের মেধা যেন আমাদের রাষ্ট্রের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে তার জন্য তাদেরকে জায়গা করে দিতে হবে। তাদের বিকাশ ঘটানোর জন্য বিশ্বকে তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিতে হবে।
Ñ সাইদুর রহমান শাহিদ
কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
|
|
|
|

বিশ্বের মধ্যে রাশিয়া একটি মাত্র দেশ, যে ৮৮২ খ্রিস্টাব্দে জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রথম দিন থেকেই তার প্রতিবেশীদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। ১৯১৭ সালে সে এমন এক মতবাদের প্রয়োজন অনুভব করলো, যা একের পর এক রাজ্য দখল এবং সেগুলো নিজ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূক্ত করে নেয়ার ঐতিহাসিক আকাক্সক্ষা নিয়মসিদ্ধ করবে, যার লক্ষ্যই হচ্ছে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া- যতক্ষণ না পৃথিবী শান্তি, বেপরোয়া হত্যা, যুদ্ধ, হাঙ্গামা এবং খুনোখুনি দ্বারা বশীভূত হয়। ক্ষমতা দখলের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী সিংহ (রাশিয়া) শৃগালরূপী জনতাকে প্রতারণা করে। তারা ঝোঁপের মধ্যে ওঁৎ পেতে থাকে অথবা গুপ্ত কক্ষে লুকিয়ে থাকে এবং এমন সুনিপুন দক্ষতার সাথে সমস্ত গোপন খেলা চালিয়ে যায় যে, ক্ষমতার লাটিম ঘুরতে ঘুরতে তাদের হাতেই চলে আসে। রাশিয়া তার প্রতিবেশীদের পদানত করার এই সর্বনাশা তৃষ্ণা এখনও পর্যন্ত প্রশমিত হয় নি। এই তৃষ্ণা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশমিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তৃষ্ণার্ত কণ্ঠ স্বশব্দে-সজোরে তার পেটকে বিদীর্ণ করে দেবে। তখন এই চির তৃষ্ণার্ত রুগিটি যা অবৈধপন্থায় জড়ো করে লোভাতুরভাবে, অধৈয্যের সাথে নির্বিচারে মুখে পুরে দিয়েছে, সেই সব অস্বাস্থ্যকর ও অস্বাভাবিক তরল পদার্থগুলি ভয়ানকভাবে ভেতর থেকে উছলে পড়তে শুরু করবে। রুশ সাম্রাজ্যবাদ ভেতর থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে; তার কোন চিহ্নই আর কেউ খুঁজে পাবে না। ভিতরের লাভার উদগীরণ আর বাইরে হাতুড়ের প্রহার-এটা আগামীকালের সূর্যোদয়ের মতই স্বতঃসিদ্ধ, অবিসাংবাদী।
ইউক্রেন যুদ্ধ সাতটি মাস পেরিয়ে গেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন উভয় পক্ষই সৈন্য যেমন হারিয়েছে তেমনি অনেক বে-সামরিক নাগরিকও হারিয়েছে। দুই দেশের অনেক মানুষ হতাহত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এই যুদ্ধের ফল ভোগ করতে হচ্ছে পুরো বিশ্বকে। মূল্যস্ফীতির দাপটে বাড়ছে ক্ষুধার্ত আর দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। অসহায় হয়ে পড়ছে বিশ্বের মধ্যবিত্তরা। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ইতোমধ্যেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। হাজার-হাজার মানুষের প্রাণ হারানো এবং এত শঙ্কা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা সামান্য যুদ্ধ বিরতির মতো আশার আলোও দেখা যায়নি। বরং অন্ধকার যেন আরো গাঢ় অন্ধকারে রূপ নিচ্ছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার অত্যাসন্ন। কারণ যুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে কেউই হার মানতে চান না। রাশিয়া বলছে, এই যুদ্ধ কেবল ইউক্রেনের বিরুদ্ধে নয়, এই যুদ্ধ ন্যাটো তথা পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে। কারণ পুতিনের সমর্থকরা পশ্চিমা বিশ্বকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙা এবং রাশিয়াকে অবনত করে রাখার কারিগর হিসেবে মনে করে।
পরাজিত রাশিয়া পশ্চিমা বিশ্বকে শক্তিশালী করবে বহুগুণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গ্রেট পাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড়ে চীনকে পেছনে ঠেলে দিবে এই পরাজয়। রাশিয়া দুর্বল হয়ে পড়লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তা এনে দিবে এক সুবর্ণ সুযোগ। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বেইজিংয়ের উপর ওয়াশিংটনের ছড়ি ঘোরানোর দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে। ইউক্রেনে রাশিয়ার জয় একদিকে যেমন পশ্চিমের পতন ডেকে আনবে, অন্য দিকে তা শি-জিংপির তাইওয়ান বশীভূতকরণ স্বপ্নকে সত্যিতে পরিণত করার রশদ জোগাবে। ইউক্রেনে পুতিন বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারলে তা তাইওয়ানের ওপর শির আক্রমণের ক্ষেত্রে নজির হিসেবে কাজ করবে। আর এর ফলে বিশ্বব্যাপি ডেকে আনবে এক বিশাল পরিণতি। বৈশ্বিক ব্যালেন্স অব পাওয়ার পূর্ণনির্ধারিত হবে নতুন করে; তৈরি হবে নতুন বিশ্ব। বিগত সাত মাস ধরে চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাস রাশিয়ার মুহুর্মুহু আক্রমণে ইউক্রেন দিশেহরা হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে তাদের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা বিশ্ব এবং ন্যাটোর সাহায্যে সাম্প্রতিক ইউক্রেন তাদের কিছু অঞ্চলে আবার নিজেদের আধিপত্য পূনোরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। রাশিয়া আধিকৃত বেশ কিছু অঞ্চল দখলমুক্ত হওয়ার ফলে জেলনস্কির ইউক্রেন মুচকি হাসছে বটে; কিন্তু এই “আপাত সাফল্যে” চিন্তায় ভাজ ফেলেছে পশ্চিমা শক্তির কপালে। কারণ চলমান যুদ্ধ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে, যখন কঠিন বিপদ চোখ রাঙাচ্ছে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। ইউরোপসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধারণা করছে, কোণঠাসা হওয়ার ফলে মরিয়া পুতিন পারমাণবিক, রাসায়নিক বা জৈবিক অস্ত্রের পথে হাটতে পারেন। পুতিন যদি সত্যিই পারমাণবিক অস্ত্র হাতে তুলে নেন, তবে তা হবে খুবই উদ্বেগজনক। একই শঙ্কার কথা বলেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, যুদ্ধে ধরাশয়ী কিংবা তীব্র অবজ্ঞার স্বীকার হলে তা নিরূপায় পুতিনকে যে বৃহৎ ধ্বংসযজ্ঞের পথে চালিত করবে না এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। পুতিনকে ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা প্রণয়ন করলে আমেরিকা এবং গোটা ইউরোপের সমূহ ক্ষতির কথা বিবেচনা করে কেউ ঝুঁকি নিতে চাইছে না। বিশেষত ইউরোপের অর্থনীতিতে নাভিশ্বাস তুলবে ক্রেমলিন পালটা ব্যবস্থার মাধ্যমে। ব্যক্তিগত বাড়ি, দোকান কিংবা কারখানা থেকে শুরু করে জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইউরোপবাসী পড়বে চরম বিপদে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার বিপরিতে রাশিয়ার পাল্টা ব্যবস্থার কারণে ইতোমধ্যে ইউরোপে বিস্ফোরণ ঘটছে জ্বালানী খাতে-গ্যাস ও তেল অনেকটা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।
চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বলয়কে শক্তিশালী করেছে। ন্যাটোকে করেছে পুনরুজ্জীবিত। শক্তিশালী করেছে ট্রান্স-আটলান্টিক সম্পর্ক। সর্বোপরি পশ্চিমা বিশ্বকে এনে দাঁড় করেছে এক শামিয়ানার নিচে। পশ্চিমারা আজ অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি একত্রিত; বিধায় আজ তারা অনেক বেশি শক্তিশালী। অন্যদিকে, রাশিয়া এই যুদ্ধে কিছুতেই পশ্চিমা শক্তির কাছে হেরে যেতে নারাজ। প্রয়োজনবোধে পারমাণবিক হামলা করতেও পিছপা হবে না। বস্তুত, ইউক্রেন যুদ্ধে পরাজিত হলে কিংবা সল্প সময়ের ব্যবধানে পুতিন চুড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে ব্যর্থ হলে তাতে করে রাশিয়া দুর্বল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠবে বিশ্ব রাজনীতিতে। এক্ষেত্রে পুতিন ও শি-জিংপিয়ের পরিকল্পনা বড় ধাক্কা খাবে। এজন্য রাশিয়ার পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে সে সম্ভাব্য সবকিছু করতে দ্বিধা করবেন না এটা নির্দ্ধিধায় বলা যায়।
আকাশের তীক্ষ্ম নখর বাজ পাখি আর সাগরের হিংস্র হাঙ্গর কি পারে ধৈর্য্য ধারণ করে অপেক্ষা করতে? জঙ্গলের চিতা আর সিংহ কি কখনো আলোচনা ও বির্তকে মিলিত হয়? শহরের সমাজবিরোধিরা কি দৃঢ় মত ও বিশ্বাসে আস্থাশীল হয়? যে মুহুর্তে একটা পশু ক্ষিপ্ত হয়, তখন সে তার সহিংস আচরণ প্রদর্শণ ছাড়া আর কিছুই জানে না। বর্তমান আমেরিকা এবং রাশিয়ার অবস্থা হয়েছে দুটি হিংস্র প্রাণীর মত; যখন যে ক্ষিপ্ত হয় তখন তার তীক্ষ্ম নখের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয় অনেক নিষ্পাপ প্রাণী। ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, ইয়ামেন, সিরিয়া, সুদান, চেচনিয়া, বসনিয়া, ইউক্রেনসহ প্রভৃতি দেশসমূহ তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। বস্তুত, বাজপাখি-বাজপাখির সাথে, শুকুন-শকুনের সাথে, শিয়াল-শিয়ালের সাথে, বাঘ-বাঘের সাথে, কাক-কাকের সাথে একত্রে বসবাস করে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বাজের সাথে সিংহ আর শকুনের সাথে শিয়ালের বসবাস শুরু হলে সেখানে শান্তির সংসার হয় না; নানান রকমের বিপত্তি ঘটে, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অস্থির হয়ে ওঠে আশেপাশের পরিবেশ।
ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সংঘাতময় হয়ে ওঠেছে পুরো পৃথিবী। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামাদা বাজতে শুরু হয়েছে। যদি সত্যিই রাশিয়া পারমাণবিক বোমার আঘাত হানে তাহলে কমপক্ষে ৫০০ কোটি মানুষ নিহত হবে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন। যদি রাশিয়া কখনো আমেরিকার উপনিবেশে পরিণত হয়, তাহলে বিশ্ব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। কারণ পারমাণবিক ধ্বংস যজ্ঞের যে ভয়াবহ আশঙ্কা আজ সারা বিশ্বে আতংকের ঝড় তুলছে, তার অবসান ঘটবে। পারমাণবিক ভয়াবহ অমানিশার অন্ধকার ও আতংকের পরিবর্তে বিশ্ববাসী দেখবে শান্তি ও স্বস্তিভরা নব-উষার স্বর্ণালি সূর্যোদয়।
|
|
|
|

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড কোনো সাধারণ অভ্যুত্থানের ঘটনা ছিল না। এটি ছিল জাতীয় চেতনাকে ধ্বংস করা বা দেশকে পুনরায় পিছিয়ে দেবার একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্তের অংশ। এই একই চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় সংঘঠিত হয় ৩ নভেম্বরের জেল হত্যাকান্ড। এসব হত্যাকান্ড কোনো বিচ্ছিন্ন বা কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। পরাজিত শক্তি বাঙ্গালি জাতির মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দেবার সুগভীর চক্রান্তের অংশ হিসেবেই এসব হত্যাকান্ড ঘটায়। পরাজিত শক্তি বলতে আমি শুধু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের যারা সরাসরি বিরোধিতা করেছিল বা পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিল তাদের বুঝাচ্ছি না। ১৯৪৮ সালেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তান নামক অদ্ভূত রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ বা বাঙ্গালির অধিকার অর্জন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠি প্রথমেই আমাদের মাতৃভাষার উপর আঘাত হানে। পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু বাঙ্গালিদের ভাষা বাদ দিয়ে তারা উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তখন বাঙ্গালিরা তীব্র প্রতিবাদে ফেঁটে পড়ে। একে একে অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্যগুলো সাধারণ মানুষের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, পরবর্তীতে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচন এবং তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ এই ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে ঘটে যেতে থাকে। বাঙ্গালির প্রতিটি আন্দোলনেই কিছু বাঙ্গালি বিরোধিতা করে। বাঙ্গালিরা যাতে কখনোই তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে না পারে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠি সেই চেষ্টাই করেছে। বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি না। মুক্তিযুদ্ধ বলি বা অন্য যে কোনো আন্দোলনের কথাই বলি না কেনো আমরা কখনোই শতভাগ ঐক্যবদ্ধ ছিলাম না। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও কিছু মানুষ এর বিরোধিতা করেছে। বঙ্গবন্ধু যখন ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন তখন অনেকেই এর বিরোধিতা করেছে। ছয় দফার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত ’৭০-এর নির্বাচনে ২৩.৭৪ শতাংশ বাঙ্গালি ভোটার নৌকা মার্কার বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল। যখন রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হয় তখনও বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ করার পক্ষে ছিল। ১০ জন বুদ্ধিজীবী এর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছেন এবং ৪০ জন বুদ্ধিজীবী এর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন। ১৯৫৪ সালের যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনের সময় থেকেই যারা এই অঞ্চলের মানুষের মুক্তবুদ্ধির কথা বলতেন, যারা প্রগতির কথা বলতেন বা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার স্বপ্ন দেখতেন তাদের ভারতের চর বা দালাল বলা হতো। অপবাদ দেয়া হতো যে, ভারতীয় চরেরা এ দেশে ইসলামকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে। তারা পাকিস্তানি শাসকদের যে কোনো কাজকেই ইসলামের সঙ্গে যুক্ত করে বৈধতা দেবার চেষ্টা করতো। পুরো পাকিস্তান আমল জুড়ে এই অবস্থা বিরাজ করে। তারা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হয়নি। ১৯৭১ সালে এসে তারা সরাসরি পাকিস্তানি দখলদার সামরিক জান্তার পক্ষে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। রাজাকার-আলবদর বাহিনী তৈরি করে তারা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করে। এদের অনেকেই পরবর্তীতে যুদ্ধাপরাধি হিসেবে মানবতা বিরোধি অপরাধের অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর মনে করা হয়েছিল এই পরাজিত গোষ্ঠি হয়তো তাদের ভুল বুঝতে পেরে দেশ গঠনে অংশ নেবে। কিন্তু তারা তা না করে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশেও তাদের অপকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে এই গোষ্ঠিটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে আমাদের এই দেশে যে সব প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি ছিল, যারা বাঙ্গালি অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য সব সময় সচেষ্ট ছিল তারা ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে বাঙ্গালির হাজার বছরের ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক চেতনা এবং মূল্যবোধের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি ক্ষমতাসীন হয়ে পুরো চিত্রটি পাল্টে দেয়। তারা আবারো পাকিস্তানি ভাবধারায় দেশ পরিচালনা করতে শুরু করে। রাতারাতি ‘বাংলাদেশ বেতার’ হয়ে যায় ‘রেডিও বাংলাদেশ’। ‘জয় বাংলার’ বদলে চলে আসে ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্য সচিব রাজাকার বাহিনীর সৃষ্টিকর্তা রাওফরমান আলীর ঘনিষ্ট সহচর শফিউল আলম হন কেবিনেট সচিব। আইয়ুব ইয়াহিয়ার প্রিয় ব্যক্তি কাজী আনোয়ারুল হক হলেন খুনি মোস্তাকের উপদেষ্টা। জেনারেল ওসমানী হলেন উপদেষ্টা, মাওলানা ভাসানীও খোন্দকার মোশতাককে অভিনন্দন জানালেন। ’৭০ এর দশকে পুরো দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটছিল। তখন বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক ব্লক এবং পুঁজিবাদি শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। যে কারণে বিভিন্ন দেশে প্রায়শই সামারিক অভ্যুত্থান ঘটতো। কিন্তু সে সব সামরিক অভ্যুত্থানের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির জনককে হত্যার মাধ্যমে শুধু রাষ্ট্র ক্ষমতায় পরিবর্তন আসেনি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মূল্যবোধের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে নবীন দেশটি আমরা লাভ করেছিলাম তাকে আবারো পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। তারা বাংলাদেশের ছদ্মাবরণে পূর্ব পাকিস্তান কায়েম করে। পাকিস্তানি চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যার কবর রচিত হয়েছিল তা আবারো ফিরিয়ে আনা হলো। জামাত নেতা গোলাম আজম জেদ্দা থেকে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডে উল্লসিত হয়ে নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহবান জানান। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি প্রকাশ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তারা এই দেশটিকে মুসলিম বাংলা করার চেষ্টায় রত হয়। তারা বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণার দাবি উত্থাপন করতে থাকে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তোলা হলো। যারা মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজনীতি থেকে কার্যত নির্বাসিত হয়েছিল তাদের পুনরায় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা করা হলো। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধিদের বিচারের কাজ শুরু করেছিলেন। যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর সমর্থনে খুন, ধর্ষণ বা অন্যান্য মানবতা বিরোধি অপরাধে নিজেদের যুক্ত করেছিল তাদের বিচারের কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর সেই বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। যারা শুধু বিরোধিতার জন্য মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে,কোনো ধরনের মানবতা বিরোধি অপরাধ করেনি তাদের মাফ করে দেয়া হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত উদার মনের একজন মানুষ। তিনি ভেবেছিলেন, এদের ক্ষমা করে দিলে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে এবং দেশের উন্নয়নে নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে পারবে। কিন্তু কথায় বলে, ‘কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না।’ বঙ্গবন্ধুর উদারতাকে এরা মূল্যায়ন না করে বরং তার বিরোধিতা করতে থাকে। দেশে বহুমুখি ষড়যন্ত্র শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধে বাঙ্গালি সেনা বাহিনীর অফিসারদের মধ্য অনধিক একশত জন অংশ গ্রহণ করেন। আর পাকিস্তানি বন্দীশালা থেকে ফিরে আসে প্রায় এগারশ বাঙ্গালি সেনা অফিসার। পাকিস্তান থেকে যে সব বাঙ্গালি সেনা অফিসার ফিরে আসেন আমি বলি না তাদের সবাই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধি ছিলেন কিন্তু তারা বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনা বাহিনী যে বর্বরতা চালিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। ফলে তারা সেই ভয়াবহতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন না। ফলে তারা বুঝতে পারেনি স্বাধীনতার জন্য আমরা কি মূল্যটাই না দিয়েছি। সেনা বাহিনীর ভেতরেও পাকিস্তান ফেরৎ এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারি সেনা কর্মকর্তাদের মাঝে এক ধরনের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। স্থানীয়ভাবে কিছু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও তৈরি হলো। জাসদ নামক একটি উগ্রপন্থি রাজনৈতিক দল তৈরি হলো। তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলতে শুরু করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের লেশমাত্র তাদের মধ্যে ছিল না। জাসদের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জলিলের পরিণতি দিয়ে প্রমাণিত হয় যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলে তাদের মাঝে কিছুই ছিল না। মেজর জলিল(অব:) মৃত্যুর আগে খেলাফৎ মজলিশে যোগদান করেন এবং পাকিস্তানে গিয়ে মারা যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় শুধু যে জামাত-আল বদররাই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তা নয়, যারা চিনাপন্থি কমিউনিষ্ট পার্টির কোনো কোনোটি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। তাদের এই বিরোধিতা মুক্তিযুদ্ধের পরও অব্যাহত থাকে। ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় বিজয় দিবস পালনের সময় সিরাজ শিকদার এবং তার দল বিজয় দিবসকে ‘কালো দিবস’ ঘোষণা করে ঢাকা শহরে হরতালের ডাক দেয়। মওলানা ভাসানী তাদের সেই ঘোষণাকে সমর্থন জানায়। স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র সব মিলিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি ও জাসদের গণবাহিনী একের পর এক থানা লুট ও দখল করতে থাকে। রক্ষী বাহিনীর সাথে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। হরতাল, ব্যাপক বোমা হামলা, রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা, সরকারি স্থাপনায় হামলা, পাটের গুদামে আগুন ইত্যাদি তৎপরতা ব্যাপক ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের পনেরই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সারা দেশে এক ধরনের থমথমে অবস্থা চলতে থাকে। সেনা বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। কারণ জুনিয়র কয়েক জন অফিসার গিয়ে বঙ্গভবন দখল করে। তারা অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলকারি খোন্দকার মোস্তাককে দিয়ে নানা ধরনের অন্যায় কাজ করাচ্ছিল। সামরিক বাহিনীর মধ্য থেকে কিছু অফিসার যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তারা সামরিক বাহিনীতে চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারা ক্রমশ শক্তিশালি হয়ে উঠতে থাকেন। যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল বা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিল তাদের মনে ভয় ঢুকে যায়, যদি সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরে আসে, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি আবার যদি ক্ষমতাসীন হয় তাহলে তাদের বিপদ হতে পারে।
বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর সেনা বাহিনীতে যদি শৃঙ্খলা ফিরে আসে, সংবিধান যদি পুন:স্থাপিত হয় এবং জাতীয় সংসদ কার্যকর হয় তাহলে সংসদের নেতৃত্বে কারা আসবে এসব প্রশ্ন দেখা দেয়। অভ্যুত্থানকারিরা বুঝতে পারে জেলখানায় বন্দি ৪ জাতীয় নেতা বেরিয়ে আসবে এবং তারাই জাতীয় সংসদ ও সরকারের নেতৃত্ব দেবে। এই ৪ জাতীয় নেতা সম্পর্কে তাদের ভীতি ছিল। কারণ নানাভাবে চেষ্টা করে, চাপ দিয়ে এমন কি প্রলোভন দেখিয়েও এই চার নেতাকে তারা সরকারে নিতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এই চার নেতা ৯ মাস যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কাজেই তাদের নেতৃত্বের গুনাবলি এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অভ্যুত্থানকারিরা সচেতন ছিল। বঙ্গবন্ধুর কোনো কোনো অনুসারি অভ্যুত্থানকারিদের সঙ্গে হাত মেলালেও এই চার জাতীয় নেতা ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা। কাজেই অভ্যুত্থানকারিরা তাদের বাঁচিয়ে রাখার সাহস করেনি। তারা বুঝতে পেরেছিল এই চার নেতাকে বাঁচিয়ে রাখা হলে এক সময় এরা বিপদের কারণ হতে পারে। এ ছাড়া এদের জনপ্রিয়তাও ছিল আকাশচুম্বি। অভ্যুত্থানকারিরা বঙ্গভবনে বসেই এই চার নেতাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নির্মম হত্যাকান্ড বিরল। জেলখানার কোনো জাতীয় নেতাকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনা বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে নজীরবিহীন। জেলখানায় ৪ জাতীয় নেতাকে হত্যার ঘটনার সঙ্গে আমি মুক্তিযুদ্ধকালিন সময়ের ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের মিল খুঁজে পাই। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি এবং তাদের স্থানীয় দোসররা যখন দেখলো স্বাধীনতা কোনো ভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না তখন তারা জাতিকে মেধাশূণ্য করার জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গভবনে অবস্থানকারি বিপথগামি সেনা কর্মকর্তারা যখন দেখলো মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির পাল্টা অভ্যুত্থান ঠেকানো যাচ্ছে না যখন তারা জেলখানায় বন্দি ৪ জাতীয় নেতাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং নির্মমভাবে তা বাস্তবায়ন করে। এই হত্যাকান্ডের জন্য খোন্দকার মোস্তাকের অনুমোদন ছিল। হত্যাকারিরা জেলখানায় যাবার পর জেলার তাদের বাধা দিয়েছিলেন। পরে জেলার মোস্তাকের সঙ্গে কথা বললে তিনি (মোস্তাক) বলেন, তারা যা করতে চায় তা করতে দিন। কোনো ধরনের বাধা দেবেন না। জেল হত্যাকান্ড কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। এটি ছিল একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রেরই অংশ। উল্লেখ্য মেজর ফারুক ও রশিদ দুই মাস আগে পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার পুন:প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হলে কারাগারে বন্দী চার নেতাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনায় খন্দকার মোশতাকের সম্মতি ছিল। তখন বঙ্গভবনেই থাকতো ফারুক, রশিদরা। এমনকি রশিদ রাষ্ট্রপতির মর্যাদার গাড়ীটিও ব্যবহার করতেন।
৩ নভেম্বর ভোর রাতে ডিআইজি প্রিজন বঙ্গভবনে ফোন করলে রশিদই ফোন ধরেন। রশিদ খন্দকার মোস্তাকের নিকট ফোনের রিসিভার হস্তান্তর করেন। মোস্তাক ফোন ধরে বেশ কিছুক্ষণ শান্তভাবে শুনে বললেন হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। উপায়ন্তর না দেখে মোসলেউদ্দিন ও তার দলকে আর বাধা দেয়ার চেষ্টা করেননি। তাজউদ্দিন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক সেলেই ছিলেন। পাশের অন্য সেলটিতে ছিলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এএইচএম কামরুজ্জামান। তাদের একটি সেলে জড়ো করে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিন জন সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। অবশেষে রক্তক্ষরণে মারা যান তাজউদ্দিন আহামদ। অভ্যুত্থানকারিরা এই চার নেতাকে বাঁচিয়ে রাখাটাকে নিরাপদ মনে করেনি। তাই তাদের হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা আর জেল হত্যা একই সূত্রে গাঁথা। জেল হত্যাকান্ডের মাধ্যেমে হত্যার রাজনীতি শেষ হয়নি।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার অনিবার্য ধারাবাহিকতা হচ্ছে একই বছরের ৩ নভেম্বর জেল হত্যাকান্ড। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে যে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল তা পরবর্তীতেও অব্যাহত রয়েছে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে জননেত্রী শেখ হাসিনার উপর বোমা হামলাসহ বিভিন্ন সময় তাকে হত্যার যে সব চেষ্টা চালানো হয়েছে তা সেই ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ডের ধারাবাহিকতা বলেই আমি মনে করি। এমন কি এক এগারোর সময় দৃশ্যত দুই নেত্রীকে দেশ থেকে বের করে দেবার যে প্রচেষ্টা (আসলে শেখ হাসিনাকেই শেষ করে দেবার চেষ্টা হয়েছিল) আমরা লক্ষ্য করি তাও সেই একই হত্যা ষড়যন্ত্রেরই ধারাবাহিকতা। ১৫ আগস্ট যারা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল তাদেরই আত্মীয়-স্বজন ব্রিগেডিয়ার বারি, বিগ্রেডিয়ার আমিন পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে নিয়েছিল এক এগারোর পর। এই মহলটি এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় নিয়ে যাবার জন্য। আজকে আমরা যাদের জঙ্গি বলি এরা কারা? বলা যেতে পারে এদের তো ১৯৭১ সালে বা ১৯৭৫ সালে জন্ম হয়নি। কিন্তু আপনি বিশ্লেষণ করলে দেখবেন এরা সেই পাকিস্তানি ভাবধারা অনুসরণ করে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে। আমি এটা জোর দিয়ে বলতে পারি, বাংলাদেশে পাকিস্তানি ভাবধারার মানুষের অভাব নেই। বর্তমানে যে জঙ্গিবাদের উত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে এদের টার্গেটও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাজার বছরের শ্বাশত বাঙ্গালির চেতনা এবং মূল্যবোধ ধারন করে চলেছেন। তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারক এবং গণতন্ত্রের মানস কন্যা। এসব কারণে জঙ্গিরা শেখ হাসিনাকেই বার বার টার্গেট করছে।
মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উপর বারবারই আঘাত এসেছে। এই আঘাত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আরো শানিত করেছে। যে কোনো প্রতিবন্ধকতা এলেই জাতীয়তা বোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শানিত হয়। কারণ সব কিছু স্বাভাবিকভাবে চললে সেখানে চেতনা ততটা কাজ করে না। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা এলেই চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। বারবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উপর আঘাত এসেছে বলেই আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ক্রমশ শানিত হচ্ছে। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে যুদ্ধাপরাধি ও মানবতা বিরোধিদের বিচারের প্রসঙ্গটি। এই বিচার কার্য শুরু হলে নানামুখি ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। বিচার বাধাগ্রস্থ হবার শঙ্কা দেখা দিলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তির উদ্যোগে সৃষ্টি হয় গণজাগরণ মঞ্চ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করার জন্যই গণ জাগরণ মঞ্চ সৃষ্টি হয়। এটা হঠাৎ করেই সৃষ্টি হয়নি। এভাবে যখনই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উপর আঘাত এসেছে তখনই মানুষ নতুন করে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কাজেই বলা যায়, যতবারই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উপর আঘাত আসবে ততই এই চেতনা শানিত হবে।
অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়
ও সাবেক উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ^বিদ্যালয়।
|
|
|
|

অনামিকা রায়
দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে জঙ্গিহামলার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, পূজাকে কেন্দ্র করে জঙ্গি হামলা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব রটিয়ে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টি করার শঙ্কা রয়েছে। তবে, এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ কাজ করছে বলেও জানান তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই ডিএমপি কমিশনারের এই শঙ্কাকে ঘিরে একধরনের আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।
বিগত কয়েকবছর ধরেই পরিলক্ষিত হচ্ছে দুর্গাপূজা এলেই দেশে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়। পুজো শুরুর আগেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিমা ভাঙচুর করে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ভীতি ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিমা ভাঙচুর থেকে শুরু করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনাও আমরা দেখেছি। বিগত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, একদল উগ্র ধর্মান্ধ লোক প্রতিহিংসার বর্শবর্তী হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের আনন্দ আয়োজনে বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে। তাইতো পুজো এলেই আনন্দের বদলে একধরনের আতঙ্ক বিরাজ করে মনে। সারাক্ষণই একটা শঙ্কা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়, এই বুঝি কোনো উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হতে হবে।
গত বছর কুমিল্লার একটি মন্দিরে পবিত্র কোরআন শরিফ রাখা নিয়ে সারাদেশে যে ধরনের অস্হিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা সহজে ভুলে যাওয়ার নয়। বিশেষ করে নোয়াখালীতে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল, যে আতঙ্ক থেকে ভুক্তভোগীরা এখনো বের হতে পারেনি। ওই ঘটনার জেরে ১০টি নিরীহ মানুষকে জীবন দিতে হয়েছিল তখন। এবছরও ওইরকম কোনো ঘটনা ঘটবে না, এরকম কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরং পুজো শুরুর আগেই কয়েকটি স্থানে প্রতিমা ভাঙচুরের যে খবর পাওয়া গেছে, তাতে সেই আশঙ্কা তো থেকেই যায়।
প্রশাসন তথা নিরাপত্তাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে এমন সতর্কতা জারি করা হলে সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে আতঙ্কিত না হয়ে তো উপায় নেই। আর তা যদি হয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য, তাহলে তো কথাই নেই।
দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে আয়োজন করতে এবছর সরকার থেকে নিরাপত্তার নানা শর্ত দেয়া হয়েছে পূজা উদযাপন কমিটিগুলোকে। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে – ১. দেশের প্রতিটি পূজাম-পে সিসি ক্যামেরা লাগানোসহ নিরাপত্তার বিভিন্ন শর্ত বাধ্যতামূলক করা। ২. প্রতিটি পূজাম-পের জন্য আয়োজকদের সার্বক্ষণিক স্বেচ্ছাসেবক দল রাখতে হবে এবং তাদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন ধরনের গুজবের ব্যাপারে। ৩. পূজাম-পের স্বেচ্ছাসেবকদের বাধ্যতামূলকভাবে হাতে আর্মব্যান্ড পড়তে হবে। ৪. গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত পূজার আয়োজকদের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি করতে হবে। ৫. আজানের সময় পূজাম-পে বাদ্যযন্ত্রের শব্দ সহনীয় রাখতে হবে।
আর সরকারের পক্ষ থেকেও যেসব ব্যবস্থা নেয়া হবে- ১. প্রতিটি পূজাম-পে ২৪ ঘণ্টায় পালাক্রমে দু`জন করে আনসার মোতায়েন থাকবে। ২. সেজন্য সারাদেশে ৩২ হাজারের বেশি পূজাম-পের জন্য এক লাখ ৯২ হাজার আনসার মোতায়েন করা হচ্ছে। ৩. পুলিশ এবং র্যাব অব্যাহত টহলে থাকবে। ৪. সব পূজাম-পে গোয়েন্দা নজরদারি রাখা হবে এবং মনিটর করা হবে ফেসবুকসহ সামাজিক মাধ্যম। ৫. পুলিশের সদর দপ্তর এবং জেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম খোলা হবে এবং ২৪ ঘণ্টা সেখানে যোগাযোগ করা যাবে। ৬. এছাড়া ভ্রাম্যমাণ আদালত রাখা হচ্ছে।
দূর্গাপূজা উপলক্ষে সরকারের নেয়া পদেক্ষপগুলো অবশ্যই আশাজাগানিয়া। কিন্তু সবচেয়ে লজ্জা এবং সেই সঙ্গে উদ্বেগের বিষয় হলো, হাজার বছর ধরে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একে অপরের পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা আবহমান বাংলার সম্প্রীতির এই দেশে নির্বিঘ্নে উৎসব পালন করতে এখন কয়েক স্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়। ধর্মীয় লেবাসধারী স্বার্থান্বেষী একটি মহল প্রতিবছরই ওৎ পেতে থাকে হিন্দু সম্প্রদায়ের এই উৎসব আয়োজনকে ধুলিস্যাৎ করতে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে সারাদেশে অস্হিতিশীল পরিবেশ তৈরি করার পায়তারায় থাকে তারা।
কিছুদিন পরপরই দেখা যায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রতিবেশী কোন হিন্দু ব্যক্তির নামে ধর্মীয় উস্কানিমূলকমূলক পোস্ট দিয়ে একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও প্রার্থনালয়ে হামলা ও লুটপাট চালানো হয়। এই সবগুলো ঘটনার ক্ষেত্রেই পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে হয় অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নামে সৃষ্ট আইডিটি ভুয়া অথবা আইডিটি হ্যাক করা হয়েছে। অথচ দুঃখজনক যে, প্রতিটি ঘটনায় প্রমাণিত হওয়ার আগেই অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে জামিন অযোগ্য আইসিটি আইনে মামলা দেয়া হচ্ছে এবং দিনের পর দিন বিনা অপরাধে ওই ব্যক্তিকে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছে।
সেক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ জানানো হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত না হলেও নিরাপত্তার স্বার্থে তাকে আটক রাখা হয়েছে। অথচ একটি ঘটনায়ও প্রকৃত অপরাধীদের বিচার করতে দেখা যায়নি, এমনকি সচরাচর গ্রেপ্তার হতেও দেখা যায় না। প্রকৃত অপরাধীর বিচার নিশ্চিত করতে পারলে এই ঘটনার বারবার পুনরাবৃত্তি হতো না বলেই সচেতন নাগরিকরা মনে করেন। কেন এমন হয়? এ ধরনের অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের সরকারগুলো রাজনৈতিক লাভ লোকসানের হিসেব-নিকেশ করে থাকেন বলে অভিযোগ আছে। অথচ একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক তো আইনের চোখে সমান। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাষ্ট্র কঠোর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হলে, এসমস্ত সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস রোধ করা সম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িক মনস্ক মহলটি যখন নিশ্চিত থাকে যে, ধর্মের নামে সন্ত্রাস করলে, এর কোন বিচার হয় না বা রাষ্ট্র কোন ব্যবস্থা নিতে সাহস করবে না, তখনই সাম্প্রদায়িকতা সমাজ ও রাষ্ট্রে আরও শক্তপোক্তভাবে শেকড় গাড়তে সুযোগ পায়, অপরাধীরা ভয় পাওয়ার বদলে উৎসাহ পায়।
সমাজের নানা স্তরে সহিংসতা ও অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। এর মধ্যে আমরা দেখেছি, শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে হেনস্তা করা হয়েছিল তার ছাত্রদের দ্বারা। হৃদয় চন্দ্র ম-লকে হেনস্থা করল তাঁর ছাত্ররা, স্বপন বিশ্বাসকে জুতার মালা পরিয়ে হেনস্তা করা হলো তাঁর ছাত্রদের দ্বারা। উৎপল কুমারকে পিটিয়ে মেরে ফেলল তাঁরই এক ছাত্র। এরকম আরও অনেক ঘটনা আছে। উপরোক্ত ঘটনাগুলো লক্ষ করলে, এক ভয়ঙ্কর সময় চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কেন-না, আজকের এসব ছাত্র-ছাত্রীরাই এদেশের ভবিষ্যত নাগরিক হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করবে। মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় নেমে আসছে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে। আমরা কি এখনো সতর্ক হবো না?
১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পরবর্তীকাল থেকেই এদেশে হিন্দু সম্প্রদায় একধরনের চাপের মধ্যে রয়েছে। পাকিস্তান আমলে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল রাষ্ট্রের কাছে সন্দেহভাজন দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। রাষ্ট্রীয় নানা চাপ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়ে অনেক পরিবারকে ওই সময় দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালে বিভিন্ন উস্কানিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করে অগণিত মানুষের প্রাণনাশের মতো লজ্জাকর ও নৃশংস ঘটনা আমরা সকলেই জানি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদেরকে `ভারতের দালাল` বলে অভিহিত করা হয়েছে। নানা অজুহাতে তাদের বাড়িঘরে হামলা করে জিনিসপত্র লুট করা হয়েছে। অনেক এলাকায় তাদেরকে জোর করে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে, যা এখনো চলমান। অথচ ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠনে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেছে তারাও।
মুক্তিযুদ্ধে যে দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি হয়েছিলো, তার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মা-বোনেরাও ছিল, এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এসে অত্যন্ত বেদনার সাথে দেখতে হচ্ছে এদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন, তাদের হাহাকার আজও থামেনি। অথচ যে চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম তার একটি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা।
ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান অধিকারে মাথা উঁচু করে এদেশে বসবাস করবে এমনটাই কথা ছিল। কথা ছিল, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার অঙ্গীকার নিয়ে আবির্ভূত এ রাষ্ট্রে সকল ধর্মের মানুষ নির্বিঘ্নে, শান্তিতে, স্বস্তি নিয়ে যার যার ধর্মীয় উৎসব পালন করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বাধীন বাংলাদেশেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের এই দুর্ভোগ থামেনি। নানা অজুহাতে তাদের বাড়িঘরে হামলা চালানো হয়, আগুন দেয়া হয় তাদের ঘর, দোকান এমনকি তাদের ধর্মীয় উপসানলয়ে। বাংলাদেশে প্রায় স্বাধীনতার পর থেকেই একশ্রেণির উগ্র ধর্মান্ধ ব্যক্তি গুজব রটিয়ে সারাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালিয়ে দেশে এক অস্হিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করে আসছে। এদের সাথে আরেক শ্রেণির পরধনলোভী বেপরোয়া মানুষের দেখা পাওয়া যায়, যাদের মূল লক্ষ্য থাকে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পদের উপর। যেন যেকোন অজুহাতে একবার প্রতিবেশীকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে পারলেই তার সমস্ত সম্পত্তি হাত করা যাবে। এসব ধর্মান্ধ, পরধনলোভী মানুষরূপী অমানুষের জন্য বারবার অবিচার-অন্যায়ের শিকার হতে হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের।
সকল ধর্মেরই মূল বার্তা শান্তি প্রতিষ্ঠা। কোন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মানুষ তার প্রতিবেশীর প্রতি নির্দয় আচরণ করে শান্তি পেতে পারে না। কিন্তু আমাদের এ অঞ্চলে সেটি প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। যুগ যুগ ধরে এদেশে আমরা পরস্পরের সহযোগিতায় ও পারস্পরিক নির্ভরতার মাধ্যমেই বেঁচে থাকি। আমাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা একে অপরের উপর নির্ভর করেই জীবন ধারণ করি। দোকানি, যানচালক বা ব্যবহার্য পণ্যের আমদানিকারক ও ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কত ধর্মের, কত জাতের, কত সংস্কৃতির মানুষের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে, তার হিসেব কে দিবে? না, তার হিসেব আমরা কেউ করতে যাই! ভালোমানের মিষ্টি খেতে হলে তো সেই হিন্দু ময়রার দোকানেই ভিড় করতে হয় আমাদের, আবার বিরিয়ানি খাওয়ার জন্যে মুসলমানের দোকানে পা না দিয়ে উপায় নেই।
আধুনিক চিকিৎসাসেবা থেকে শুরু করে মুঠোফোন ও ইন্টারনেট বা কম্পিউটার, একালের এসব আবশ্যিক হয়ে ওঠা প্রয়োজনীয় অধিকাংশ সামগ্রীর আবিষ্কারক বা উৎপাদক কিন্তু মুসলিম নন। এদেশের অনেকেই দেশের তুলনায় ভারতের হিন্দুধর্মাবলম্বী চিকিৎসকের পরামর্শে চিকিৎসা নিতে ভালোবাসেন। তাছাড়া দেশেও প্রচুর হিন্দু ডাক্তার আপন মেধা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। বাস্তবে আমরা এক বিশ্ব সম্প্রদায়ের অংশ, তাকে অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। এর কোনো অংশের ক্ষতিসাধন মানেই নিজেরই অনিষ্ট ডেকে আনা। ক্ষণিকের সামান্য লাভের আশায় দীর্ঘদিনের বহু মানুষের অবদানে তৈরি সম্প্রীতির এই বন্ধন নষ্ট করা মানে নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনা।
ধর্ম আর রাজনীতি একাকার হয়ে গেলে সমাজে প্রকৃত ধর্ম টিকিয়ে রাখা যায় না। ধর্ম তো শান্তির কথা বলে, নীতি-নৈতিকতার কথা বলে। সেই ধর্মের নামে অরাজকতা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি আর তৈরি না হোক। প্রতিটি সম্প্রদায় স্বাভাবিক পরিবেশে নিঃশঙ্ক চিত্তে আনন্দের সাথে তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব পালন করুক। ক্ষমতা, সম্পদ আর অর্থের মোহের কাছে ধর্ম খুবই তুচ্ছ হয়ে যায়। একটি গোষ্ঠীর কাছে ধর্ম তখন কেবলই স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহারের উপকরণে পরিণত হয়। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলোকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে, এ অবস্থা থেকে তারা পরিত্রাণ চান কি-না। নাগরিকদের ভাবতে হবে, ঠিক কীধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে তারা বসবাস করতে চান। হিংসা-বিদ্বেষের বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে উঠুক। মনে রাখতে হবে, "নগরে আগুন লাগলে দেবালয় এড়ায় না"।
লেখক : সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মী।
|
|
|
|

জসিম উদ্দিন তুহিন:
উলুধ্বনি, শঙ্খ, কাঁসর আর ঢাকের বাদ্যিতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে শনিবার ((১ অক্টোবর)) সকাল থেকে। শারদীয় দুর্গোৎসবের আজ মহাষষ্ঠী। বুধবার (৫ অক্টোবর) বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে পাঁচ দিনের এ মহোৎসব।
বৈশ্বিক মহামারি করোনার প্রাদুর্ভাবে গত দু`বছর অনেকটাই নিষ্প্রাণ ছিল বাঙালি হিন্দুর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। আলোকসজ্জাসহ উৎসবসংশ্নিষ্ট বিষয় পরিহার করে কেবল `সাত্ত্বিক পূজায়` সীমিত রাখা হয়েছিল আয়োজন; ছিল বাড়তি সতর্কতা ও স্বাস্থ্যবিধি মানার বিষয়গুলোও। তবে এবার করোনার সংকট ও ভয় কাটিয়ে ফিরে এসেছে চিরচেনা সেই উৎসবের আমেজ। সারাদেশের মণ্ডপ-মন্দিরে বর্ণাঢ্য উৎসবের প্রস্তুতিও এখন শেষ হয়েছে।
এ বছরের দুর্গাপূজার নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, আজ শনিবার ষষ্ঠীতে দশভুজা দেবী দুর্গার আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মধ্য দিয়ে শুরু হবে পূজার আনুষ্ঠানিকতা। ষষ্ঠী তিথিতে আজ সকাল সাড়ে ৬টার মধ্যে দেবীর ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভ ও ষষ্ঠীবিহিত পূজা। সায়ংকালে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মধ্য দিয়ে শুরু হবে মূল দুর্গোৎসব। এদিন সকাল থেকে চণ্ডীপাঠে মুখরিত থাকবে সব মণ্ডপ এলাকা। আগামীকাল রোববার মহাসপ্তমী, ৩ অক্টোবর মহাষ্টমী ও কুমারীপূজা এবং ৪ অক্টোবর মহানবমী শেষে ৫ অক্টোবর বিজয়া দশমী ও প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে পাঁচ দিনের দুর্গোৎসব।
তবে শুক্রবার পঞ্চমীর সন্ধ্যায় বোধনের মধ্য দিয়ে দেবীর আগমনধ্বনি অনুরণিত হতে শুরু করেছে। সারাদেশের পূজামণ্ডপগুলোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে দেবীর বোধন। শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে এই বোধনের মাধ্যমে দক্ষিণায়নের নিদ্রিত দেবী দুর্গার নিদ্রা ভাঙার জন্য বন্দনা করা হয়। মণ্ডপে-মন্দিরে পঞ্চমীতে সায়ংকালে তথা সন্ধ্যায় এই বন্দনা অনুষ্ঠিত হয়।
শনিবার সকাল ৮টার দিকে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে দেবীর ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ষষ্ঠীর দিনের পূজা। সিদ্ধেশ্বরী ছাড়াও ঢাকা ও সারা দেশের সব মন্দিরের প্রায় কাছাকাছি সময়ে শুরু হয়েছে ষষ্ঠীপূজার আয়োজন। এ সময় ঢাকঢোলের বাজনা, কাঁসা, শঙ্খের আওয়াজ এবং ভক্তদের উলুধ্বনিতে দেবী দুর্গাকে পৃথিবীতে স্বাগত জানানো হয়। সন্ধ্যায় হবে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস। বোধন অর্থ জাগ্রত করা। মর্ত্যে দুর্গার আবাহনের জন্য বোধনের রীতি প্রচলিত রয়েছে।
এদিকে পূজা উপলক্ষে নতুন রূপে সেজে উঠেছে ঢাকেশ্বরী মন্দিরসহ রাজধানীর অন্যসব মন্দির। ঢাকা মহানগরের মধ্যে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের প্রধান আকর্ষণ থাকে এই মন্দির। সেই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের মন্দিরেও দুর্গাপূজায় থাকছে বিশেষ আয়োজন। ঐতিহ্যবাহী বনানী মাঠে আয়োজিত দুর্গা মণ্ডপে সাজানো হয়েছে আরও সুন্দর রূপে।
প্রতিবারের মতো এবারও প্রস্তুত করা হয়েছে মহামায়া দেবী দুর্গাসহ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশসহ বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমা। সন্ধ্যায় ভক্ত ও দর্শনার্থীদের জন্য বাহারি সব রং দিয়ে সাজানো হয়েছে এসব প্রতিমা। রং- বেরঙের আলোকসজ্জা আর নানা রঙের ডিজাইনের কাঠামো দিয়ে সাজানো হয়েছে পুরো পূজাঙ্গন।
সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, গুলশান-বনানী সর্বজনীন পূজা ও পুরান ঢাকার সব মন্দিরগুলোতে সন্ধ্যারতি, ধূনচী নাচসহ পূজার পাঁচ দিনই থাকছে নানা আনুষ্ঠানিকতা। এ ছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন, মিরপুর কেন্দ্রীয় মন্দির, শাঁখারীবাজার, রমনা কালীমন্দির।
পুরান অনুযায়ী, এবার দেবী মর্ত্যে এসেছেন গজে চেপে। পুরাণ অনুযায়ী, দুর্গা গজে চড়ে এলে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনেন। আর ৫ অক্টোবর বিজয়া দশমীতে দেবী মর্ত্য ছাড়বেন নৌকায় চড়ে। নৌকায় গমনেও ধরনী হবে শস্যপূর্ণ তবে থাকবে অতিবৃষ্টি বা বন্যা।
|
|
|
|
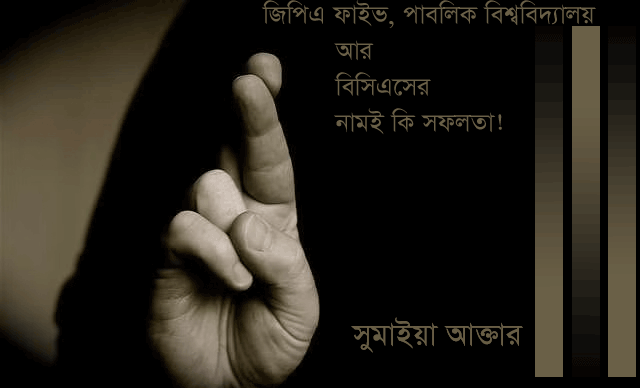
সুমাইয়া আক্তার
একটা সময় ছিল যখন আমাদের জীবনে পড়াশোনাটাই মূল লক্ষ্য ছিল না। শৈশবের দুরন্তপনায় যখন আমরা মেতে থাকতাম। জীবনে কোন কিছুর প্রতি আমরা কোন চাপ নিতাম না। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে যাওয়া ক্লাস শেষে বাড়ি ফিরে খেলার মাঠে দৌড়। হাসি তামাশা আর রংধনুর মতোই রঙিন জীবন বেনীআসহকলা`র মত পার করতাম আমরা।
আমাদের বেড়ে ওঠার সাথে সাথে যেন বদলে যেতে থাকলো সেই দুরন্তপনার শৈশব। পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে বর্তমান যুগের শিশুদের শৈশবে। ভিন্নতা দেখা দিয়েছে আমাদের সে যুগ আর বর্তমান যুগের শিশুদের জীবন যাপনে।
বর্তমান যুগের শিশুদের জন্মের পরই কেড়ে নেওয়া হয় তাদের সুন্দর শৈশবটাকে। আর নামিয়ে দেয়া হয় এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায়। শৈশবের মাঠে হেসেখেলে পার করার দিনগুলোতে তাদের ক্লাস, কোচিং আর প্রাইভেট টিউটরের কাছে উৎসর্গ করতে হয়। এই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় তাদের নামিয়ে দিয়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত করছি তাদের সুস্থ স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনটাকে। জীবনে আসলে পড়ালেখাই মুখ্য বিষয় না। পড়াশোনার পাশাপাশি চিত্তবিনোদনের ও যথেষ্ট দরকার আছে। মানসিক বিকাশের জন্য চিত্তবিনোদন অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমান যুগের বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে সে সময়টা দিতে চান না। জন্মের তিন বছর পরই তাদের পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হয় এক গাদা বই। যার ভার বহন করতে গিয়ে সোনালি শৈশবটাকে মলিন করে তুলতে হচ্ছে ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশুদেরকে।
জিপিএ- ৫ নামক এক অসুস্থ সফলতার দিকে হেঁটে চলেছে বর্তমান সমাজ। এখনকার যুগের বাবা-মায়েদের নাকি সম্মান জড়িয়ে থাকে সন্তানদের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ রেজাল্টের উপর। কোনোভাবে যদি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারে তাহলে শুরু হয় কোমলমতি শিশুদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। আর এগুলো কারা করে? তাদের বাবা-মায়েরা-ই। বর্তমান যুগের বাবা-মায়েরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা মানতে চান না। তারা চান এমন সন্তান যারা সারা দিন-রাত পড়ার টেবিলে বসে পড়ুক। প্রত্যেক বাবা -মা-ই চায় তাদের সন্তান ক্লাসে ফার্স্ট হোক। প্রত্যেকটি পাবলিক পরীক্ষায় যেন জিপিএ-৫ পেয়ে উর্ত্তীণ হয়। আবার কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে সাধারণ বৃত্তি কেন পেল, ট্যালেন্টপুলে কেন পেল না তা নিয়েও অনেক অপমান অত্যাচার করা হয়। প্রায়শই খবরের কাগজে দেখা মিলে এমন কিছু মর্মান্তিক ঘটনার যেখানে "জিপিএ-৫ না পাওয়ায় স্কুল শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা" এ ধরনের শিরোনাম দেখা যায়।
এই জিপিএ-৫ এর জন্য একের পর এক কোচিং, প্রাইভেট, এক্সট্রা ক্লাসে পাঠানো হয় তাদের। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জীবনে ও অবসর থাকে। কিন্তু এখনকার যুগের বাচ্চাদের জীবনে কোনো অবসর থাকে না। খেলাধুলা, ব্যায়াম, ঘুরাঘুরি এগুলো এখনকার বাবা-মাদের মতে সময় নষ্ট। আর এসব করে সময় নষ্ট করার চেয়ে তারা এখন তাদের সন্তানকে পড়ার টেবিলে বসিয়ে রাখতে চায়। তাদের মতে এতে তাদের সন্তান সবার চেয়ে এগিয়ে যাবে। কিন্তু বোকা বাবা-মা একবারও ভেবে দেখে না যে তারা আসলে এভাবে তাদের সন্তানের জীবন ও ভবিষ্যত নষ্ট করছে। ধ্বংস করছে শিশুদের শৈশব, কৈশোরের রঙিন দিনগুলো। বাধা সৃষ্টি করছে শিশুদের মানসিক বিকাশে। জিপিএ-৫ নামক এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলতে থাকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত। বাবা-মায়েরা সন্তানদের এক্সট্রা ক্লাস, কোচিং, প্রাইভেট এর জন্য দিয়ে তাদের দিনের বাকি অংশ কেড়ে নেন। এমনকি রাতের বেলায় ও অনেকে তাদের প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ান। যে কোনো মূল্যেই চাই এক হালি জিপিএ-৫।
উচ্চমাধ্যমিকের পর জিপিএ-৫ এর সেই অসুস্থ প্রতিযোগিতা-ই শেষ নয়। এরপর তাদের সম্মুখীন হতে হয় আরো বড় যুদ্ধের। যার নাম ভর্তি যুদ্ধ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সিট সে যেন সোনার হরিণ।দিন দিন এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সারা বাংলাদেশের সকল সরকারি মেডিক্যাল, সরকারি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সব মিলিয়ে মাত্র ৬৪,০০০ আসন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের তুলনায় আসন সংখ্যা খুবই নগণ্য। আর এই সীমিত আসন দখল করার জন্য প্রতিবছর ভর্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী। উচ্চমাধ্যমিকের পর ছুটি কাটাবে তো দূরের কথা কলেজে পড়াকালীন সময়েই একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের ভর্তি প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করতে হয়। এইচএসসির পর তা শুরু হয় পুরাদমে। একের পর এক প্রাইভেট, কোচিং, বই আর এক গাদা শীটের মাঝেই ডুবে থাকতে হয় সারাদিন। কঠোর পরিশ্রম করার পরও অনেক শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।
জীবন দিয়ে পড়াশোনা করেও অনেক সময় সবার ভাগ্য সহায় হয় না। যেহেতু শিক্ষার্থীদের তুলনায় আসন সংখ্যা খুবই কম তাই সবাই পরিশ্রম করলেও চান্স পাবে না। কিন্তু এটা আমাদের সমাজ, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন মানতে চায় না। তাদের মতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পেলে তার কোনো কোয়ালিটিই নাই। আর যদি শিক্ষার্থী সায়েন্স ব্যাকরাউন্ডের হয় তবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সে যত ভালো সাবজেক্ট নিয়েই পড়ুক না কেন সমাজ তাকে মেডিক্যাল, বুয়েট নিয়ে প্রশ্ন করবেই। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরা যেন মুখিয়ে-ই থাকে কবে রেজাল্ট বের হবে আর পাশের বাসার ছেলে/মেয়েটা কি রেজাল্ট করলো তা জানতে হবে। আর এসব আত্নীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে নিজেদের সম্মান বজায় রাখতে বাবা-মায়েরা এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় বলি দেন তাদের কোমলমতি সন্তানদের।
সত্যি বলতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আহামরি কোনো কিছু না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলেই যদি জীবনে সফল হওয়া যেত তাহলে দুদিন পর পর ঢাবি, রাবি, জাবি, ইবি, জবি শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার খবর শোনা যেত না।
প্রাইভেট ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পড়েও বর্তমানে অনেক শিক্ষার্থী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্কিল ও টেকনোলজির দিক দিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। এমনকি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডেও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ব্রাক ইউনিভার্সিটিসহ আরো অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে।
এ তো গেল শিক্ষার প্রতিযোগিতা এরপর আসে চাকরির প্রতিযোগিতা। আমার মনে পড়ে আমি যখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাই তখনই আমার বড় কাকা আমাকে বলেছিলেন "তোকে কিন্তু বিসিএস দিতেই হবে" বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগেই আমার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিসিএসই আমার জীবনের লক্ষ্য। ভার্সিটিতে প্রায়ই ক্লাসে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বলেন যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে এত বছরেও নাকি কোনো বিসিএস ক্যাডার বের হতে পারেনি।এ কথাগুলো তারা অনেকটা আক্ষেপ নিয়েই বলেন এবং আশা করেন আমরা যেন বিসিএসে সফলতা অর্জন করে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করতে পারি। তখন আমার বলতে খুব ইচ্ছা করে যে, স্যার/ম্যাম আপনারা শুধু এটাই দেখলেন যে আমাদের বিভাগ থেকে কেউ বিসিএস ক্যাডার হতে পারেনি কিন্তু এটা দেখলেন না যে এ বিভাগের কত শিক্ষার্থী কত বড় বড় জায়গায় দায়িত্বরত আছে। তাদের মতে বিসিএসই যেন চূড়ান্ত সফলতা। এছাড়া যেন আর কোনো চাকরির কোনো দাম নেই। বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন একেকটা বিসিএস ক্যাডার গড়ার কারখানা হয়ে উঠেছে।
বর্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা জীবনকে উপভোগ করার বদলে প্রথম বর্ষ থেকেই হাতে এমপি থ্রী নিয়ে ঘুরছে। মনে পড়ে এপিজে আবুল কালাম স্যারের সেই বিখ্যাত উক্তি, "যতদিন শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু চাকরি পাওয়া হবে ততদিন সমাজে চাকররা জন্মাবে মালিক নয়।" সত্যিই এখন আমরা ভুলে গেছি যে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন, মনুষত্ববোধ জাগ্রতকরণ, সুনাগরিক হওয়া। তা ভুলে আমরা এখন মুখস্থবিদ্যার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছি।
ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাতে আমাদের সকলের এখনই সোচ্চার হওয়া উচিত। জীবন তো একটাই সে এক জীবনকে নরকের বদলে উপভোগ্য করে তুলতে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। শিশুদের পর্যাপ্ত মানসিক বিকাশের জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি পর্যাপ্ত খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও ভ্রমণে সময় দেওয়া উচিত। শিশুদের উপর কোন চাপ সৃষ্টি না করে তাদের মতামতকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া উচিত। তবেই ঘটবে মানসিক বিকাশ জাগৃত হবে মনুষ্যত্ববোধ এবং জীবন হবে সুন্দর ও উপভোগময়।
লেখক: সুমাইয়া আক্তার
শিক্ষার্থী গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
|
|
|
|

জসিমউদ্দিন তুহিন
প্রতিটি জাতির রয়েছে নিজস্ব শিল্প ও সংস্কৃতি। একেকটি শিল্পের বিস্তারের পেছনে রয়েছে দেশ বা জাতির অবদান। আমাদের দেশের অন্যতম শিল্প হচ্ছে মৃৎশিল্প। আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মৃৎশিল্পের সম্পর্ক অনেক গভীর। ‘মৃৎ’ শব্দের অর্থ মৃত্তিকা বা মাটি আর ‘শিল্প’ বলতে এখানে সুন্দর ও সৃষ্টিশীল বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। এজন্য মাটি দিয়ে দিয়ে তৈরি সব শিল্পকর্মকেই মৃৎশিল্প বলা যায়। প্রাচীনকাল থেকে বংশানুক্রমে গড়ে ওঠা গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প আজ বিলুপ্তির পথে। আজকাল কুমারপাড়ার মেয়েদের ব্যস্ততা অনেক কমে গেছে। কাঁচামাটির গন্ধ তেমন পাওয়া যায় না। হাটবাজারে আর মাটির তৈজসপত্রের পসরা বসে না। তবে নির্মম বাস্তবতার সঙ্গে যুদ্ধ করে এখনো কিছু জরাজীর্ণ কুমার পরিবার ধরে রেখেছেন বাপ-দাদার এই ব্যবসায়।
মৃৎশিল্পের সঙ্গে চীনের বড় একটা ঐতিহ্য আছে। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জানা গেছে চীনের বিখ্যাত শহর থাংশান-এ মৃৎশিল্পের জন্ম হয়েছিল। আর এ কারণেই এ শহরটিকে মৃৎশিল্পের শহর বলা হয়। চীনের অন্যতম প্রাচীন শহর পেইচিং থেকে ১৫০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এই শহরটি। এই শহরের পথে-প্রান্তরে, বিনোদন কেন্দ্র বা পার্কগুলোতে মৃৎশিল্পের বিভিন্ন শিল্পকর্ম দেখতে পাওয়া যায়। থাংশানের মৃৎশিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশের সূত্রপাত মিং রাজবংশের ইয়ুং লে-এর সময়কালে। এ শহরের রয়েছে প্রায় ৬০০ বছরের ইতিহাস। এখানে নানা ধরনের চীনামাটির ৫০০টিরও বেশি মৃৎশিল্প রয়েছে। এখানকার বিভিন্ন রকম মাটির মধ্যে প্রাচীন স্থাপত্য চীনামাটি, স্বাস্থ্যসম্মত চীনামাটি, শিল্পায়ন চীনামাটি, হাইটেক চীনামাটি, শিল্পকলা চীনামাটি ইত্যাদি অন্যতম। বিভিন্ন দোকানে গিয়ে অনেক ক্রেতা এখনো চীনের তৈরি জিনিসপত্র খোঁজ করেন।
চীনা শিল্পের যেমন ঐতিহ্য আছে, ঠিক তেমনি আমাদের দেশেরও আছে। শত শত বছর ধরে এই শিল্পের সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ জড়িত আছেন। আমাদের দেশে এই ধরনের কাজের সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে আমরা কুমার বলি। অতীতে গ্রামের সুনিপুণ কারিগরের হাতে তৈরি মাটির জিনিসের কদর ছিল অনেকাংশ বেশি। পরিবেশ বান্ধব এ শিল্প শোভা পেত গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে আজ তা হারিয়ে যেতে বসেছে। মাটির তৈরি কলসি, ফুলের টব, সরা, বাসন, সাজের হাঁড়ি, মাটির ব্যাংক, শিশুদের বিভিন্ন খেলনাসমগ্রী নানা ধরনের তৈজসপত্র তৈরি করত কুমারেরা। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ এঁটেল মাটি, জ্বালানি কাঠ, শুকনো ঘাস, খড় ও বালি।
আমাদের দেশে এই শিল্পের ব্যবহার সেই আদিকাল থেকে। পোড়ামাটির নানাবিধ কাজ, গৃহস্থালির নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি, পুতুল, খেলনা, প্রতিমা, প্রতিকৃতি, টপ, শো-পিসসহ অসংখ্য জিনিস আজও কুমারশালায় তৈরি হয়ে ক্রেতাদের চাহিদা মেটাচ্ছে। কথিত আছে, কাউকে মাটির তৈরি হাঁড়ি কিংবা গণেশের মূর্তি দিলে বিনিময়ে ওই পাত্রে বা মূর্তির পেটে যত চাল ধরে ততটাই দেওয়া হতো শিল্পীকে। মাটির তৈরি বিভিন্ন রকমারি আসবাবপত্র চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি আজ প্রচুর চাহিদা লক্ষণীয়। তাছাড়া মেয়েদের বিভিন্ন মাটির তৈরি গয়না সহজেই চোখে পড়ে দেশের মেলাগুলোতে এছাড়া বিভিন্ন দোকানে।
আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে আজ মাটি দিয়ে প্রস্তুত অনেক কিছুই হারিয়ে যেতে বসেছে। তার পরও অনেক সংগ্রাম করে পোড়ামাটির গৃহস্থালির নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি, পুতুল, খেলনা, প্রতিকৃতি, শো-পিসসহ অসংখ্য জিনিস কুমারশালায় তৈরি হচ্ছে। পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া পেশা টিকিয়ে রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কুমারদের। এ সম্প্রদায়ের লোকজনেরা মাটির তৈরি করা পাকপাতিল, ঠিলা, কলসি, পুতুল, কুয়ার পাট, খেলনার সামগ্রী, ফুলের টব, মাটির ব্যাংক ইত্যাদি হাটবাজারে বা গ্রামে গ্রামে বড় ঝাঁকা বোঝাই করে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন। ছয় মাস ধরে তারা মৃৎশিল্প তৈরি করে আর ছয় মাস বিভিন্ন কায়দায় বিক্রি করতেন।
মৃৎশিল্প আমাদের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছে। ২০০০ সালের পর বেড়ে যায় রফতানি। এখন ইউরোপ ও আমেরিকা ছাড়াও নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় রফতানি হচ্ছে বাংলাদেশের পণ্য। রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে ভারত, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনাম। বিদেশে মূলত মাটির তৈরি পামিজ, ফুলের টব, বিভিন্ন ধরনের গার্ডেন প্রডাক্ট, নাইট লাইট, ডাইনিং আইটেম, ইনডোর গার্ডেন আইটেম, ফুলদানি, মাটির টব ও মাটির ব্যাংকের চাহিদা আছে। ব্যাপক ভিত্তিতে মাটির তৈরি জিনিস রপ্তানি করা গেলে আরো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যেত।
বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোর অন্যতম হচ্ছে মৃৎশিল্প। এটি শুধু শিল্প নয়, আবহমান গ্রামবাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য। মাটির নান্দনিক কারুকার্য ও বাহারি নকশার কারণে এই শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে যাতে বাইরের রাষ্ট্রে রপ্তানি করা যায় তার জন্য আরো বেশি করে উদ্যোগ নিতে হবে। মৃৎশিল্পের সঙ্গে জড়িত কুমার এবং পালদের সহজ শর্তে ঋণ এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্নমুখী উৎপাদন বাড়াতে হবে। এই দেশীয় শিল্পের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে ।
লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট
|
|
|
|
|
|
|